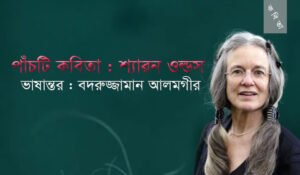পর্তুগালের নোবেলজয়ী লেখক হোসে সারামাগো । এমদাদ রহমান
প্রকাশিত হয়েছে : ০৯ অক্টোবর ২০২২, ৩:০৭ পূর্বাহ্ণ, | ১০৩৬ বার পঠিত

হোসে সারামাগো পর্তুগালের লেখক; রাজধানী লিসবন থেকে উত্তর-পূর্বদিকের আজিনহাগা গ্রামের এক ভূমিহীন কৃষক পরিবারে, ১৯২২ সালের ১৬ নভেম্বর তাঁর জন্ম। লিসবনে কখনও তিনি মোটর মেকানিক, কখনও অনুবাদক, সাহিত্য সমালোচক, সাংবাদিক ইত্যাদি পরিচয়ে বেড়ে উঠেছেন। সাহিত্যে নোবেল পেয়েছেন ১৯৯৮-এ। ১৯৪৭-এ মাত্র ২৪ বছর বয়সে সারামাগোর প্রথম উপন্যাস ‘ল্যান্ড এন্ড সিন’ প্রকাশিত হয়। ৭৭-এ বের হয় দ্বিতীয় উপন্যাস ‘ম্যানুয়াল অব পেইন্টিং অ্যান্ড ক্যালিগ্রাফি’। ৮২ সালে ‘বালতাসারা অ্যান্ড ব্লিমুন্ডা’ উপন্যাসটি প্রকাশিত হলে হোসে সারামাগো আন্তর্জাতিক পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর বহুল আলোচিত-সমালোচিত দুটি উপন্যাস—‘দি ইয়ার অব দ্য ডেথ অব রিকারদো রিয়েস’, ‘দ্য গসপেল অ্যাকোর্ডিং টু জেসাস ক্রাইস্ট’। সারামাগো-র অন্য উপন্যাস হচ্ছে—‘অল দ্য নেমস’, ‘দ্য স্টোন ক্রাফ্ট’, ‘ব্লাইন্ডনেস’। ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত ‘ব্লাইন্ডনেস’ উপন্যাসটি তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনা হিসেবে স্বীকৃত। আজীবন টাইপরাইটারে লিখেছেন নোবেলজয়ী এই ঔপন্যাসিক। ১৯৯২ সালে পর্তুগালের ডানপন্থী সরকার ‘দ্য গস্পেল অ্যাকোর্ডিং টু জেসাস ক্রাইস্ট’ বইটিকে ধর্মবিরোধী আখ্যা দিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য পুরস্কারের তালিকা থেকে বাদ দিলে প্রতিবাদস্বরূপ তিনি স্পেনে স্বেচ্ছা নির্বাসনে চলে যান। সেখানে, ২০১০ সালের ১৮ জুন, ৮৭ বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
হোসে সারামাগো-র এই ‘আর্ট অব ফিকশন সাক্ষাৎকারটি ‘দ্য প্যারিস রিভিউ’-এ ১৯৯৮ সালের শীত সংখ্যায় হিসেবে প্রকাশিত। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছিলেন— দনজালিন বাখোসো।
সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী: লিসবনের কথা খুব মনে পড়ে?
 হোসে সারামাগো: মনে পড়া আর না পড়া ইত্যাদি দিয়ে ব্যাপারটিকে পুরোপুরি ব্যক্ত করা যাবে না; লিসবনের কথা মনে পড়া যখন অনিবার্য হয়ে পড়বে, যেভাবে কবিরা বলে থাকেন নস্টালজিয়া সম্পর্কে, নস্টালজিয়ার যে অনুভূতিটি একেবারে হাড়ে এসে বিঁধে, লিসবনকে মনে পড়ার ব্যাপারটিও সেরকম। কিন্তু আমি হাড়ের মধ্যে তেমন তীব্র কোনো অনুভূতি টের পাই না।
হোসে সারামাগো: মনে পড়া আর না পড়া ইত্যাদি দিয়ে ব্যাপারটিকে পুরোপুরি ব্যক্ত করা যাবে না; লিসবনের কথা মনে পড়া যখন অনিবার্য হয়ে পড়বে, যেভাবে কবিরা বলে থাকেন নস্টালজিয়া সম্পর্কে, নস্টালজিয়ার যে অনুভূতিটি একেবারে হাড়ে এসে বিঁধে, লিসবনকে মনে পড়ার ব্যাপারটিও সেরকম। কিন্তু আমি হাড়ের মধ্যে তেমন তীব্র কোনো অনুভূতি টের পাই না।
বিষয়টি নিয়ে মাঝে মাঝে আমি ভেবেছি। লিসবনে আমার বন্ধুদের অনেকেই এখনও আছেন, সেখানে কিছুদিন আগে আমরা খুব অল্প সময়ের জন্য গিয়েও ছিলাম। কিন্তু এখন লিসবন নিয়ে আমার যে সংবেদন, যে বেদনা, তাতে আমি সত্যিই জানি না যে এই শহরের আর কোথায় আমি যাব! লিসবনে গিয়ে আমি কী করব তাও এখন আর জানি না।
মাত্র কয়েকটি দিনের জন্য কিংবা এক বা দুই সপ্তাহের জন্য লিসবনে গেলে আমি আবারও সেই পুরোনো অভ্যাসগুলো ফিরে পাই যেন পুরোনো দিনগুলোতেই ফিরে এসেছি কিন্তু আমি তো চাই-ই যত দ্রুত সম্ভব এখানে লিসবনে ফিরে আসতে। এই শহর আর তার অধিবাসীদের আমি ভালোবাসি। এখানে আমি নিজের মতো করে থাকতে পারি। আমি যে এই শহর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাব তাও ভাবতে পারি না। হ্যাঁ, সবকিছুর পর সত্য হচ্ছে, সবাই একদিন সবকিছু ছেড়ে চলে যায়, কিন্তু আমি যে যাব সেটা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে।
সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী: বহু বছর ধরে যেখানে বসবাস করেছেন, লেখালেখি করেছেন, একদিন স্মৃতিময় সেই জায়গাটি ছেড়ে ল্যানযেরোয় চলে এলেন, এখানে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছেন? লেখার পুরোনো জায়গাটির কথা মনে পড়ে না?
সারামাগো: এখানে, নিজেকে খুব সহজেই খাপ খাইয়ে নিয়েছি। আসলে আমি এমন এক ধাঁচের লোক নিজের জীবনকে যে দুর্বোধ্য করে না। জীবনকে অতিনাটকীয় না করেই আমি বেঁচে থেকেছি, জীবনকে যাপন করেছি। ভালোমন্দ যাই ঘটুক না কেন আমি কেবল সেই মুহূর্তগুলোতেই বেঁচে থাকতে চেয়েছি। আর হ্যাঁ, আমি যদি দুঃখ পেতে শুরু করি তাহলে সেই দুঃখকে অনুভবও করতে পারি, কিন্তু… আমি অন্যভাবে বলতে চাই, জীবন খুব আকর্ষণীয় হয়ে উঠুক আমি হয়তো তা চাইনি!
আমি এখন একটি বই লিখছি। বইটি লিখতে গিয়ে আমি কেমন যাতনা ভোগ করছি, চরিত্র নির্মাণে কীরকম বিরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছি, কমপ্লিকেটেড ন্যারেটিভের সূক্ষ্ম দ্যোতনা সম্পর্কে কীভাবে জানতে পারছি—আপনাকে এ সম্পর্কে কিছু বলাটা অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার হবে। আসলে বোঝাতে চাইছি, আমি সেটাই করব যতটুকু করা আমার পক্ষে সম্ভব। লেখালেখি সবসময়ই আমার কাছে কাজ। কাজ থেকে লেখালেখিকে কোনোভাবেই আমি আলাদা ভাবতে পারি না; আমি মনে করি, লেখা ও কাজ দুইয়ে মিলে আসলে একই ব্যাপার। লেখা ও কাজের পরস্পরের সঙ্গে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। শব্দগুলোকে আমি পর পর লিখে যাচ্ছি, একের পর এক কিংবা একটি শব্দের পাশে বসিয়ে দিচ্ছি অন্য আর-একটি শব্দ, গল্পটিকে বলতে গিয়ে, কিংবা আমার ভেতরের সেইসব কথাকে অবিরাম লিখে চলেছি যাকে আমি তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেই মনে করি; অন্ততপক্ষে আমার নিজের কাছে তো কথাগুলো মূল্যবান। লেখালেখির নিরন্তর প্রক্রিয়াটিকে আমি কাজ হিসেবে ধরে নিয়েছি।
সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী: লেখার কাজ কখন করেন? প্রতিদিনই কি লেখেন?
 সারামাগো: লেখাটিতে, সেটা উপন্যাস হোক বা অন্য কিছু, আমি যখন পুরোপুরি ডুবে যাই, তখন দরকার নিরবচ্ছিন্নতা। অবিরাম লিখতে থাকার দরকার হয় যখন, তখন প্রতিদিনই লিখি। বাড়ির কিছু কাজ মাঝে মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, কোথাও যাওয়ার থাকলেও কাজে বাধা পড়ে, তখন আর অবিরাম লেখা যায় না; এসব বাদ দিলে আমি প্রতিদিন-লিখতে-বসা-লেখক, আবার আমি কিছু নিয়ম-মেনে-চলা-লেখকও। প্রতিদিন নির্দিষ্ট কয়েক ঘণ্টা লিখতেই হবে বলে নিজেকে জোর করে লেখায় বসাই না; একদিনে দুই পৃষ্ঠা—সাধারণত এই পরিমাণ লিখতে পারলেই আমার হয়ে যায়। আজ হয়তো নতুন একটি উপন্যাসের দুই পৃষ্ঠা লিখলাম, আগামীকাল লিখব আরও দুই পৃষ্ঠা। আপনার মনে হবে দিনে মাত্র দুই পৃষ্ঠা খুব বেশি তো নয়, সামান্য; কিন্তু আমাকে তো অন্য লেখাও লিখতে হবে; কিছু গদ্য, চিঠিপত্রের উত্তর; হিসেব করে দেখুন প্রতিদিন দুই পৃষ্ঠা করে লিখতে লিখতে বছরে আটশো পাতার মতো লেখা আপনার টেবিলে জমা হচ্ছে। কম কথা!
সারামাগো: লেখাটিতে, সেটা উপন্যাস হোক বা অন্য কিছু, আমি যখন পুরোপুরি ডুবে যাই, তখন দরকার নিরবচ্ছিন্নতা। অবিরাম লিখতে থাকার দরকার হয় যখন, তখন প্রতিদিনই লিখি। বাড়ির কিছু কাজ মাঝে মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, কোথাও যাওয়ার থাকলেও কাজে বাধা পড়ে, তখন আর অবিরাম লেখা যায় না; এসব বাদ দিলে আমি প্রতিদিন-লিখতে-বসা-লেখক, আবার আমি কিছু নিয়ম-মেনে-চলা-লেখকও। প্রতিদিন নির্দিষ্ট কয়েক ঘণ্টা লিখতেই হবে বলে নিজেকে জোর করে লেখায় বসাই না; একদিনে দুই পৃষ্ঠা—সাধারণত এই পরিমাণ লিখতে পারলেই আমার হয়ে যায়। আজ হয়তো নতুন একটি উপন্যাসের দুই পৃষ্ঠা লিখলাম, আগামীকাল লিখব আরও দুই পৃষ্ঠা। আপনার মনে হবে দিনে মাত্র দুই পৃষ্ঠা খুব বেশি তো নয়, সামান্য; কিন্তু আমাকে তো অন্য লেখাও লিখতে হবে; কিছু গদ্য, চিঠিপত্রের উত্তর; হিসেব করে দেখুন প্রতিদিন দুই পৃষ্ঠা করে লিখতে লিখতে বছরে আটশো পাতার মতো লেখা আপনার টেবিলে জমা হচ্ছে। কম কথা!
এ ছাড়া আমি খুবই সাদামাটা, তেমন বিশেষত্ব কিছু নেই, তবে আমার কোনো বাজে অভ্যাস নেই, নাটকীয়তাও নেই, মোটের ওপর লেখার কাজটিকে কোনোভাবেই আমি কল্পনার রং মিশিয়ে অতিরঞ্জিত করি না। সৃষ্টির কাজে মগ্ন হয়ে আমি যে বিপন্নতার মুখোমুখি হই, যে নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করি, সে সম্পর্কে কথা বলতে চাই না। লেখার টেবিলে পড়ে থাকা না-লেখা কাগজটিকে আমি কখনও ভয় পাই না। এমনকি যে রাইটার্স ব্লকের কথা সবাই বলে, আরও যেসব সমস্যার কথা লেখকদের মুখে প্রায়ই শুনি, এসবের কোনো ভয় আমার ভেতর ক্রিয়া করে না। এসব সমস্যা আমাকে পীড়িতও করতে পারে না। কিন্তু অন্য কোনো কাজ করতে গেলেই বিপত্তি বাধে। কাজটিকে আমি যেভাবে সম্পন্ন করতে চাই তেমন সুচারুভাবে হয় না, কখনও কাজটি আমার জন্য দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। কাজটিকে আমি ঠিক যেভাবে করতে চেয়েছিলাম ঠিক সেভাবে না হলে শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে বাধ্য হই।
সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী: লেখেন কোথায়? সরাসরি কম্পিউটারেই লেখেন?
সারামাগো: হ্যাঁ, লেখাটি শুরু থেকেই কম্পিউটারে লিখি। আমার প্রাচীনকালের সেই টাইপরাইটারটিতে সর্বশেষ যে বইটি লিখেছি সেটা হচ্ছে ‘দ্য হিস্ট্রি অব দ্য সিজ অব লিসবন’। কথা হচ্ছে, টাইপরাইটার থেকে কি-বোর্ডে অভ্যস্ত হতে আমার তেমন বেগ পেতে হয়নি। প্রায়ই বলা হয় যে কম্পিউটারে কম্পোজের কাজটি একটি বিশেষ স্টাইল যেখানে লেখা থেকে কিছু একটা বাদ পড়ে যায়, লেখাটি মন মতো হতে চায় না, ভাবটিকে পুরোপুরি ধরা যায় না, কিন্তু আমি তো তা মনে করি না, কি-বোর্ডকে আমি এমনভাবে ব্যবহার করি ঠিক যেভাবে পুরোনো টাইপরাইটারটিতে লিখতাম।
কম্পিউটারে যা কিছু করছি টাইপরাইটারেও অনুরূপ কাজটিই করতাম যদি যন্ত্রটি এখনও আমার কাছে থাকত। ব্যবধান একটাই—কম্পিউটার অনেক ঝকঝকে, আরামদায়ক এবং গতিসম্পন্ন। যন্ত্রটি লেখালেখির পক্ষে সুবিধাজনক। হ্যাঁ, আমার লেখালেখির ওপর কম্পপিউটারের উদ্বেগজনক কোনো প্রভাব এখনও পড়েনি। ব্যাপারটি আসলে কাগজে হাতে লেখার বদলে টাইপরাইটারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ার মতো মামুলি ব্যাপার হিসেবেই দেখা উচিত। এতে কোনো সমস্যা আছে বলে মনে করি না। লেখকের যখন লেখার নিজস্ব শৈলী থাকে, নিজস্ব শব্দভাণ্ডার থাকে তখন কাগজ কিংবা টাইপরাইটারের পরিবর্তে কম্পিউটারে লিখলে সমস্যা দেখা দেবে কেন? এখন যেভাবেই হোক আমি কি-বোর্ডেই লেখার কাজ চালিয়ে যাব; আর খুব স্বাভাবিক যে ব্যাপারটি লেখা হয়ে যাওয়ার পর প্রিন্ট করে ফেলা; সব সময়ই যতটুকু লেখা হয়, লেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্ট করে ফেলি। প্রিন্ট না করলে তখন কেমন এক অনুভূতি হয়, যেন…
সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী: লেখাটিকে স্পর্শ করা!
সারামাগো: হ্যাঁ, পৃষ্ঠাগুলো স্পর্শ করাটাই তো মূল ব্যাপার।
সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী: প্রতিদিন দুই পৃষ্ঠা লিখে প্রিন্ট নেওয়ার পর সেখানে আর কোনো পরিবর্তন করেন?
সারামাগো: লেখা শেষ করে পুরো টেক্সটকে কয়েকবার পড়ি, তখন কিছু পরিবর্তন আসে। লেখার স্টাইল এবং ডিটেইলিং এবং কিছু বিশেষ জায়গায় কিঞ্চিৎ অদলবদল হয়। টেক্সটটিকে যথাযথ করে তুলবার জন্য আরও কিছু পরিবর্তন আসে কিন্তু সেটা কখনোই বড়ো কোনো পরিবর্তন নয়। প্রথমবারের লেখায় নব্বইভাগ কাজ আমি করে ফেলি আর শেষ পর্যন্ত তা টিকেও যায়, তেমন একটা ফেলতে হয় না। কিছু কিছু লেখক যেরকম করেন আমি কখনোই সেরকম করি না, যেমন—বিশ পাতায় গল্পটির একটি সারসংক্ষেপ লিখে ফেলা। পরবর্তীতে এই বিশ পাতাই বাড়তে বাড়তে আশি পাতায় পরিণত হবে, তারপর আশি থেকে হবে আড়াইশো। এটা আমি করি না। আমার বইটি শুরু হয় একটি বই হিসেবেই, বই হতেই সেটা ধীরে ধীরে বিস্তৃত হতে থাকে। এখন যে উপন্যাসটি লিখছি, লিখতে লিখতে উপন্যাসটির পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়িয়েছে একশো বত্রিশ, এখন আমি কিন্তু লেখাটিকে টেনে টেনে একশো আশি পাতায় নিয়ে যাবার আয়োজন করব না, তারা যত আছে ততই থাকুক। এখন হবে কী, এই পৃষ্ঠাগুলোতেই যা কিছু পরিবর্তন আসার তা আসবে, কাটাকাটি হবে; কিন্তু সেটা এমন কোনো পরিবর্তন নয়, বাদ পড়ে যাওয়া কিছু জরুরি কথা আর প্রথম খসড়ায় যা তেমন জোরালো হতে পারেনি তা অন্তর্ভুক্ত হবে, তাতে আলো পড়ছে। লেখার আঙ্গিকে, দৈর্ঘ্যে এমনকি বিষয়বস্তুতেও কোনো পরিবর্তন আসবে না। পরিবর্তনটা হবে টেক্সটের উৎকর্ষের জন্য, সৌন্দর্যের জন্য; অন্য কিছু নয়।
সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী: কোনো সুনির্দিষ্ট ধারণা থেকে লিখতে শুরু করেন?
সারামাগো: অবশ্যই। কী বলতে চাই, ঠিক কোথায় পৌঁছাতে চাই সে সম্পর্কে অবশ্যই আমার একটি পরিষ্কার ধারণা থাকে, তবে ব্যাপারটা খুব কঠিন কিছু নয়। শেষ পর্যন্ত তো সে কথাটিই বলি যা বলতে চেয়েছিলাম। প্রায়শই আমি ব্যাখ্যা দেবার কৌশলগুলো ব্যবহার করেই যুক্তি উপস্থাপন করি। আমি লিসবন থেকে পর্তোয় যেতে চাই, এটা জানি, কিন্তু এটা তো জানি না যে যাত্রাপথটি কেমন, সহজ না কঠিন। পর্তোয় যেতে হলে আমাকে আগে কাস্তেলো ব্র্যাঙ্কো পার হতে হবে, কিন্তু পার হওয়াটা জটিল, সহজ নয়; কেন-না জায়গাটি উপকূল থেকে দূরবর্তী হলেও স্পেন সীমান্তের নিকটবর্তী, আবার লিসবন এবং পর্তো উভয়ই আটলান্তিক উপকূলে…
 এখন এই কথাগুলো দিয়ে আমি যা বোঝাতে চাচ্ছি তা হচ্ছে, এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় যেতে আমাকে যে পথ পার হতে হবে সে পথ সোজা নয়, সর্পিল, ঘোরানো। গল্পের ন্যারেটিভের উৎকর্ষের জন্য এই সর্পিল যাত্রাপথ আমাকে সাহায্য করবে—প্রথম খসড়ায় বাদ পড়েছিল কিংবা লিখবার প্রয়োজনই বোধ করিনি, হয়তো-বা মাথাতেই ছিল না সেগুলো তখন লিখিত হয়ে যাবে। আগে বাদ পড়লেও এখন অনিবার্য হয়ে পড়েছে। গল্প বলার ন্যারেটিভকে, মূহুর্তগুলোকে ধরবার জন্য যা কিছু করা দরকার সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে, আর এ কথার মানে হল কোনোকিছুই পূর্বনির্ধারিত নয়। যদি গল্পটি পূর্বপরিকল্পিত থাকে, যদি সত্যিই গল্পটিকে তার সমস্ত খুঁটিনাটিসহ জেনে লিখতে বসা সম্ভব হয়, একদম শেষ বাক্যটি পর্যন্ত আগেই ভেবে রাখা হয়, তাহলে পুরো লেখাটিই নষ্ট হবে, কাজটি একেবারেই সার্থক হবে না। বইটি প্রকাশ হবার আগেই বাধ্য হবে প্রকাশিত হতে। একটি বই ধীরে ধীরে বই হিসেবে তার অস্তিত্ব লাভ করে। আমি যদি বইটিকে তার সৃষ্টির আগেই বাধ্য করি প্রকাশিত হতে তাহলে আমি এমন কিছু করছি যা একটি গল্পের গড়ে ওঠার স্বাভাবিক যেসব রীতি আছে, যে প্রক্রিয়া আছে, আমি সেই প্রক্রিয়াগুলোর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে চলে গেছি।
এখন এই কথাগুলো দিয়ে আমি যা বোঝাতে চাচ্ছি তা হচ্ছে, এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় যেতে আমাকে যে পথ পার হতে হবে সে পথ সোজা নয়, সর্পিল, ঘোরানো। গল্পের ন্যারেটিভের উৎকর্ষের জন্য এই সর্পিল যাত্রাপথ আমাকে সাহায্য করবে—প্রথম খসড়ায় বাদ পড়েছিল কিংবা লিখবার প্রয়োজনই বোধ করিনি, হয়তো-বা মাথাতেই ছিল না সেগুলো তখন লিখিত হয়ে যাবে। আগে বাদ পড়লেও এখন অনিবার্য হয়ে পড়েছে। গল্প বলার ন্যারেটিভকে, মূহুর্তগুলোকে ধরবার জন্য যা কিছু করা দরকার সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে, আর এ কথার মানে হল কোনোকিছুই পূর্বনির্ধারিত নয়। যদি গল্পটি পূর্বপরিকল্পিত থাকে, যদি সত্যিই গল্পটিকে তার সমস্ত খুঁটিনাটিসহ জেনে লিখতে বসা সম্ভব হয়, একদম শেষ বাক্যটি পর্যন্ত আগেই ভেবে রাখা হয়, তাহলে পুরো লেখাটিই নষ্ট হবে, কাজটি একেবারেই সার্থক হবে না। বইটি প্রকাশ হবার আগেই বাধ্য হবে প্রকাশিত হতে। একটি বই ধীরে ধীরে বই হিসেবে তার অস্তিত্ব লাভ করে। আমি যদি বইটিকে তার সৃষ্টির আগেই বাধ্য করি প্রকাশিত হতে তাহলে আমি এমন কিছু করছি যা একটি গল্পের গড়ে ওঠার স্বাভাবিক যেসব রীতি আছে, যে প্রক্রিয়া আছে, আমি সেই প্রক্রিয়াগুলোর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে চলে গেছি।
সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী: সবসময়ই এভাবে লেখেন?
সারামাগো: সবসময়, কারণ লেখালেখির অন্যকোনো পদ্ধতি আমার জানা নেই। আমার ধারণা লেখালেখির এই পদ্ধতিটি আমাকে শিখিয়েছে, যদিও নিশ্চিত নই এ ব্যাপারে অন্য লেখকরা কী বলবেন, আমাকে শিখিয়েছে এমন কিছু সৃষ্টি করা যার থাকবে খুব শক্ত একটি কাঠামো [স্ট্রাকচার]। আমার বইগুলোয় প্রতিটি মুহূর্ত এমনভাবে উঠে আসে যেভাবে একজন নির্মাতা বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করে তার কাঠামোটি গড়ে তোলেন যাতে নিশ্চিত পতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়; হ্যাঁ, এভাবেই একটি বই জন্ম নেয়। এই প্রক্রিয়াতে থাকে অনন্য যুক্তিশৃঙ্খল, পূর্বনির্ধারিত কোনো ভাবনা নয়।
সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী: চরিত্ররা কি কখনও চমকে দেয়?
সারামাগো: উপন্যাসের চরিত্র নিজ থেকে চলতে শুরু করবে, লেখক তাকে কেবল অনুসরণ করবেন, চরিত্রের দ্বারা তিনি চালিত হবেন—আমি এ নিয়মের ওপর আস্থাশীল লেখক নই, আমার ভিন্ন ঘরানা। লেখককে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে চরিত্রদেরকে কিছু করতে বাধ্য করা না হয়, চরিত্র যা করতে চায় তা তার ব্যক্তিত্বের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের বিপরীত না হয়ে যায়। চরিত্রের স্বাধীনতা থাকবে না। সে লেখকের পাতা ফাঁদে ধরা পড়ে যাবে। লেখক হিসেবে আমার হাতে চরিত্রটি বন্দি হয়ে থাকবে কিন্তু সে এমনভাবে বন্দি হবে যেন সে কোনোভাবেই বুঝে উঠতে না পারে যে সে ফাঁদে আটকা পড়েছে। চরিত্রের হাত-পা সব সুতোয় আটকে গেছে কিন্তু সুতোটা খুব টানটান নয়, শিথিল, ঢিলা। চরিত্রগুলো মুক্তি ও স্বাধীনতার বিভ্রমটাকে উপভোগ করতে পারবে কিন্তু তারা কখনোই কোথাও যেতে পারবে না যতক্ষণ না লেখক হিসেবে আমি তাদের সেখানে নিয়ে যাব। যখনই এমন কিছু ঘটতে শুরু করবে ঠিক তখনই লেখক সুতোয় টান দেবেন, টান দিয়েই তাদেরকে বলবেন, এখানে আমিই তোমাদের নিয়ন্ত্রণ কর্তা।
গল্পে যতগুলো চরিত্র থাকবে সবগুলোই গল্পের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। চরিত্রগুলো গল্পে এমন একটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে, গল্পের যে স্ট্রাকচারটিকে লেখক সৃষ্টি করতে চাইছেন, সেখানে লেখককে তারা সাহায্য করবে। আমি যখন একটি চরিত্রকে উপস্থাপন করি তখন আমার জানা থাকে যে এই চরিত্রটিকেই আমার দরকার; জানা থাকে তার কাছে আমি কী প্রত্যাশা করছি, তখনও কিন্তু চরিত্রটি সম্পূর্ণ দাঁড়ায়নি; একটু একটু করে সে সম্পূর্ণতা পাচ্ছে। আমিই একমাত্র লোক যে চরিত্রটিকে পূর্ণতা দেবে। এটাও কিন্তু চরিত্রের আত্ম-নির্মিতির একটি বিশেষ রীতি, যাকে আমিই গড়ে তুলছি এবং আমিই তার একমাত্র সহযাত্রী। অর্থাৎ, আমি কোনোভাবেই চরিত্রটির বিরুদ্ধে গিয়ে তার বিকাশ ঘটাতে পারব না। চরিত্রটির প্রতি আমার পূর্ণ শ্রদ্ধা থাকতে হবে, অথবা এমনভাবে শুরু করতে হবে অন্য কোনোভাবে যা সম্ভব ছিল না। এখানে উদাহরণ টেনে বলছি, আমি কখনোই এমন কোনো চরিত্রকে গড়ব না যে কোনো অপরাধে জড়িয়ে পড়বে, যদি না অপরাধ করবার মতো অবশ্যম্ভাবী এবং যৌক্তিক পরিস্থিতির জন্ম হয়। এ ছাড়া, যা জরুরি তা হচ্ছে, পাঠকের প্রতিক্রিয়া; পাঠক যদি গ্রহণ না করে তাহলে অপরাধকর্মটি কোনো মানে তৈরি করতে পারবে না।
এখন আমি আরও একটি উদাহরণ দিতে চাই। ‘বালতাসার অ্যান্ড ব্লিমুন্ডা’ হল প্রেমের উপাখ্যান, আরও স্পষ্ট করে যদি বলতে চাই, তাহলে বলতে হবে অত্যন্ত সুন্দর একটি প্রেমের গল্প। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে বইটি লেখার একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে আমি বুঝতে পারলাম ভালোবাসার শব্দগুলো না লিখেই আমি প্রেমের গল্প লিখে ফেলেছি! না বালতাসার, না ব্লিমুন্ডা পরস্পরকে সেইসব শব্দের একটিও কখনও বলেনি যাদেরকে আমরা প্রেমের শব্দাবলি হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। পাঠক হয়তো ভাবতে পারেন যে পুরো ব্যাপারটি পরিকল্পিত, কিন্তু আসলে তা নয়। পাঠক তো পরে, আমি নিজেই প্রথমে চমকে গেছি। তারপর ভেবেছি, কীভাবে সম্ভব হল? আমি একটি প্রেমোপাখ্যান লিখেছি প্রণয়ঘটিত সংলাপের একটিমাত্র শব্দেরও ব্যবহার ছাড়া!
এখন, একটুখানি কল্পনা করে নেওয়া যাক যে অদূর ভবিষ্যতে বইটির কোনো একটি পরিমার্জিত সংস্করণে আমি যদি খেয়ালখুশি মতো কিছু সংলাপ বসিয়ে দিই, গভীর প্রণয়ের কিছু শব্দ এখানে সেখানে লিখে ফেলি—তাহলে সেটা সম্পূর্ণরূপেই দুটি চরিত্রের সঙ্গে প্রতারণা করা হবে, তাদেরকে তখন মেকি আর মিথ্যা বলে মনে হবে। আমার মনে হয় বইটির বর্তমান সংস্করণটি সম্পর্কে যার জানাশোনা নেই তেমন পাঠকও তখন গল্পের দুর্বলতা ধরে ফেলতে পারবে। ঠিক কীভাবে এই দুটি চরিত্র, যারা একেবারে প্রথম পৃষ্ঠা থেকে নিজেদের সঙ্গে কথা বলছে, বইটির আড়াইশো পৃষ্ঠায় গিয়ে আচমকা তারা কীভাবে ‘আমি তোমাকে ভালোবাসি’ কথাটি বলবে?
এভাবে আমি আসলে চরিত্রের সরলতা ও সততাকে গুরুত্বসহকারে দেখার কথাটি বলছি। তাকে এমনভাবে যেন গড়ে তোলা না হয় যাতে সে তার ব্যক্তিত্ব থেকে বিচ্যুত হয়, তার আন্তর্জাগতিক মনস্তত্ত্ব থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। উপন্যসের এক একটি চরিত্র কিন্তু এক একজন স্বতন্ত্র মানুষ। ‘ওয়ার অ্যান্ড পিস’-এর ‘নাতাশা’ একজন স্বতন্ত্র মানুষ; ‘ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট’-এর রাসকলনিকভ একজন স্বতন্ত্র মানুষ; ‘দ্য রেড অ্যান্ড ব্ল্যাক’-এর জুলিয়েনও স্বতন্ত্র। বাস্তবের আমার আপনার মতই তাদের অস্তিত্ব বিদ্যমান। এভাবে এক একটি চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে সাহিত্য পৃথিবীর লোকসংখ্যা বাড়িয়ে চলে। আমরা কিন্তু এই তিনটি চরিত্রকে কখনোই সেই লোকদের মতো ভাবতে পারব না যারা আর বেঁচে নেই। জীবনের স্বাভাবিক নিয়মে যারা কিছুদিন বেঁচে থেকে মারা গেছেন—এই চরিত্রগুলো তাদের মতো নয়, কিংবা নিছক শব্দ দিয়ে রাশি রাশি কাগজে তাদের কথা লিখে রাখার মতো মামুলি কোনো বিষয় নয়। তাদেরকে আমরা সত্যিকার মানুষ হিসেবেই ভাবতে থাকি। আমি মনে করি, এটাই পৃথিবীর সমস্ত ঔপন্যাসিকের স্বপ্ন। তাদের সৃষ্ট চরিত্র যেন ‘বিশেষ কিছু’ হয়ে ওঠে আর মানুষের ভিড়ে বেঁচে থাকে।
সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী: আপনার কোনো চরিত্রকেও কি এমন বিশেষ কিছু হিসেবে দেখতে চান?
সারামাগো: এভাবে কিছু বলাটা সম্ভবত পাপ হবে, সেটা অনুমানের পাপ কিন্তু ভিতরের কথাটা, যাকে আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি সেই কথাটি বলে ফেলা উত্তম। আমি মনে করি আমার উপন্যাসের চরিত্রগুলো ‘দ্য ম্যানুয়াল অব পেইন্টিং এন্ড ক্যালিগ্রাফি’-র চিত্রকর চরিত্রটি, ‘অল দ্য নেমস’-এর সেনোর হোসে—এরা সত্যিকার অর্থেই ‘বিশেষ কিছু’। এই চরিত্রগুলো সম্পর্কে যা সত্য তা হচ্ছে, কাউকে হুবহু কপি করে তাদের গড়ে তোলা হয়নি কিংবা কারও ব্যক্তিত্বকে অনুকরণ করেও তাদের সৃষ্টি করা হয়নি। তারা এমনভাবে এই পৃথিবীতে আছে ঠিক যেভাবে আমরা বেঁচে আছি, তবে তারা উপাখ্যানের মানুষ, যাদের শুধুমাত্র শারীরিক উপস্থিতিটাই নেই। আমি তাদেরকে এভাবেই দেখি, যদিও আমরা জানি যে সাধারণত লেখকদেরকে সবকিছুকে খণ্ডিত করে দেখবার জন্য দায়ী করা হয়।
সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী: ‘অন্ধত্ব’ উপন্যাসে চিকিৎসকের স্ত্রীর চরিত্রটিকে আমার গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। পাতার পর পাতা পড়তে পড়তে চরিত্রটিকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, অন্যান্য চরিত্রের বেলাতেও ব্যাপারটি সত্য। চরিত্রগুলো ভীষণরকম জীবন্ত। অন্যদের নিয়ে তেমন কিছু আপনি বলেননি!
সারামাগো: যেখানে কোনো ধরনের শারীরিক বিবরণ আমি দিইনি সেখানে চিকিৎসকের স্ত্রীর চরিত্রটিকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন—ব্যাপারটা আমার জন্য আনন্দের। আসলে, ‘অন্ধত্ব’ উপন্যাসে কোনো চরিত্রকেই বর্ণনা করা হয়নি। চরিত্রের নাক কিংবা চিবুক দেখতে কেমন—এগুলোর সারগর্ভ বিবরণ দেওয়ার কোনো দরকার আছে বলে আমার মনে হয়নি। আমার কাছে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল পাঠক। পাঠকই চরিত্রদের গড়ে তুলবে, একটু একটু করে, তাদের নিজেদের মতো করে তারা দেখবে। এখানে লেখকের ভূমিকা হবে পাঠককে আস্থার সঙ্গে লেখাটির অংশীদার করে তোলা।
সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী: ‘অন্ধত্ব’ লেখার ধারণা কীভাবে পেয়েছিলেন?
সারামাগো: অন্য উপন্যাসগুলোর ক্ষেত্রে যেরকম হয়েছে, সেভাবে ‘অন্ধত্ব’ও একটি বিশেষ আইডিয়া থেকে বিকশিত হয়েছে, হঠাৎ করেই আমার চিন্তায় ফুটে উঠেছে। (এভাবে লিখবার এটাই যে যথাযথ পদ্ধতি সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত ছিলাম না কিন্তু এ ছাড়া ভালো কোনো উপায়ও খুঁজে পাইনি)। রেস্টুরেন্টে বসে দুপুরের খাবারের অপেক্ষা করছিলাম, হঠাৎ কী হল জানি না, ভাবতে শুরু করলাম, আমরা সবাই যদি অন্ধ হতাম? প্রশ্নটির উত্তর চিন্তা করলাম, কেন জানি মনে হল আসলে প্রত্যেকে আমরা অন্ধ, এই হল উপন্যাসটির ভ্রূণ। তারপর আমি শুধু লিখে গেছি, ঘটনাপরম্পরাকে লিপিবদ্ধ করে গেছি। একটি বিশেষ পরিণতিকে জন্ম দিতে চেয়েছি কিন্তু পরিণতিটি ছিল লোমহর্ষক, কিন্তু তাতে শক্ত যুক্তিও ছিল। কারণ ও ফলের মধ্যেকার সম্পর্কের একটি পদ্ধতিগত প্রয়োগ ছাড়া অন্ধত্বে কিন্তু কল্পনাশক্তির ব্যবহারও নেই।
সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী: আমার খুব ভালো লেগেছে। যদিও বইটি পড়ে ওঠা সহজ ব্যাপার নয়, অত্যন্ত জটিল উপন্যাস, অনুবাদটিও ভালো হয়েছে।
সারামাগো: জেভানি পোর্তিয়েরো সম্পর্কে কিছু জানেন, আমার দীর্ঘদিনের ইংরেজি অনুবাদক ছিলেন। মারা গেছেন।
সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী: মারা গেছেন?
সারামাগো: এইডসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন, এই ফেব্রুয়ারিতে। ‘অন্ধত্ব’-র অনুবাদের কাজ করছিলেন, কাজ শেষ করেই চলে গেলেন। অনুবাদ যতই শেষের দিকে যাচ্ছিল ততই তিনি উপলব্ধি করছিলেন যে অন্ধ হতে চলেছেন, চিকিৎসক যে ঔষধ দিয়েছেন তার প্রভাবে। এখন তিনি যদি চিকিৎসকের পরামর্শমতো ঔষধ খান তাহলে আরও কিছুদিন বাঁচতে পারবেন, আর না খেলে নানান জটিল শারীরিক অবস্থা তৈরি হবে। আমরা তার দৃষ্টিশক্তিকে বাঁচাতে চাইলাম। তিনি ঝুঁকি নিয়ে উপন্যাসের অনুবাদ করতে লাগলেন যার বিষয়বস্তু—মানুষের অন্ধত্ব। কী যে এক বিপর্যয়কর পরিস্থিতি ছিল, ভাবুন!
সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী: ‘দ্য হিস্ট্রি অব দ্য সিজ অব লিসবন’ লেখার আইডিয়া কীভাবে পেয়েছিলেন?
সারামাগো: লেখাটি ১৯৭২ সাল থেকে মাথায় নিয়ে ঘুরছি, মূলত একটি অবরোধ সম্পর্কিত ধারণা; শহরটিকে ঘিরে ফেলা হয়েছে কিন্তু এটা স্পষ্ট নয়ে যে কে বা কারা তা করেছে। অস্পষ্ট অবরোধের ব্যাপারটি তারপর বাস্তব একটি অবরোধের ঘটনায় বিবর্তিত হয়েছে, যা ১৩৮৪-তে কাস্তিলিয়াওদের দ্বারা লিসবন অবরোধকালীন ঘটনাবলির সঙ্গে গিয়ে মিশেছে, এর সঙ্গে আমি আর-একটি অবরোধকে যুক্ত করে দিয়েছি যা দ্বাদশ শতকে ঘটেছিল। শেষে, দুটি ঐতিহাসিক ঘটনা সমন্বিত হয়েছে—আমি অবরোধের স্থায়িত্বকাল নিয়ে কল্পনা করেছি, অবরুদ্ধ এবং অবরোধকারী প্রজন্ম নিয়ে ভেবেছি। অ্যাবসার্ড এই অবরোধ সম্পর্কে বলতে হয়—শহরটিকে ঘিরে ফেলা হয়েছিল; চারপাশে মানুষ ছিল অসংখ্য; এবং শহর থেকে বেরিয়ে যাবার পথও খোলা ছিল না।
শেষ পর্যন্ত সমস্ত কিছু মিলিত হয়ে একটি বইয়ে লিপিবদ্ধ হয়; আমি যাকে ইতিহাসের সত্যানুসন্ধানের গভীর ধ্যান বলেই ধরে নিয়েছি। ইতিহাস কি সত্য কিছু? আমরা যাকে ইতিহাস বলি তা কি অতীতের গল্পটির সম্পূর্ণ পুনঃকথন? ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে ফিকশন নয়, কারণ ইতিহাসের নির্মিতি ঘটে-যাওয়া ঘটনাভিত্তিক। যা কিছু সত্য তাই প্রকৃত ঘটনা। কিন্তু সেইসব ঘটনা-সন্নিবেশে ফিকশনের সম্ভাবনা বেশি থাকে। ইতিহাসে বাছাইকৃত সত্যকে একত্রিত করা হয় যা গল্পকে সংগতি প্রদান করে, এগিয়ে যাওয়ার পথটি নির্দেশ করে। তখন কষ্টিপাথরে যাচাই করে বহু কিছুকেই বাদ দিতে হয়। প্রকৃত ইতিহাসে এমন কিছু সত্য থাকে যা ‘লিখিত ইতিহাসে’ অন্তর্ভুক্ত হয় না কিন্তু তাই একদিন ইতিহাসকে ভিন্ন তাৎপর্য প্রদান করে। ইতিহাসকে কখনোই চূড়ান্ত হিসেবে পাঠ করা উচিত নয়। কেউ-ই এ কথা বলতে পারে না যে আমি নিশ্চিত হয়ে বলছি ঘটনাটি ঠিক এভাবেই ঘটেছিল…
‘দ্য হিস্ট্রি অব দ্য সিজ অব লিসবন’ বইটি নিছক ঐতিহাসিক রচনার খসড়া নয়। সত্য হিসেবে ইতিহাসেরই এক গভীর ধ্যান, কিংবা ইতিহাস সম্পর্কে এমন এক আন্দাজ যেখানে সত্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু মিথ্যা নয়, যদিও প্রায়শই তা প্রতারণা হয়ে যায়। জরুরি হচ্ছে একটি ‘না’-কে সঙ্গে নিয়ে সরকার-স্বীকৃত অফিসিয়াল ইতিহাসকে পাঠ করা যাতে অন্যদের খুঁজে বের করা ‘হ্যাঁ’-কে যাচাই করাটা সম্ভব হয়। এটি করতে হয় নিজেদের জীবনের সঙ্গে কল্পনাশক্তি ও মতাদর্শের মিশ্রণে। যেমন—বিপ্লব হচ্ছে একটি ‘না’; সেই না ‘হ্যাঁ’-এ রূপান্তরিত হয়। সেটা খুব দ্রুতই হয়, কখনও দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর হয়। তখন তাকে আবারও ‘না’ হিসেবে দেখতে হয়। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় ‘না’ হচ্ছে আমাদের সময়ের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় শব্দ। ‘না’ যদি কোনো ভুলও হয়, তাহলে নেতিবাচকতা থেকে ভালো কিছু নির্ণীত হয়। আজকের এই পৃথিবীকে বলছি একটি ‘না’ আজকের বাস্তবতায়, উদাহরণ হিসেবে।
এখানে বলা যেতে পারে—বইটি খুব আহামরি কিছু নয়; বইটি ছোট্ট একটি ‘না’ কিন্তু এখনও কারও জীবনে পরিবর্তন আনতে সক্ষম। বাক্যের মধ্যে একটি ‘না’ ঢুকিয়ে দিয়ে সরকার-স্বীকৃত ইতিহাস বলছে, ক্রুসেডাররা ১১৪৭-এ লিসবনকে পুনরায় জয় করবার জন্য পর্তুগাল সম্রাটকে সাহায্য করেছিল। রিমুন্দো শুধু ইতিহাসকে অন্যভাবে লিখতেই নেতৃত্ব দেননি তিনি নিজের জীবনটাকেও পরিবর্তন করার উপায়টির সন্ধান শুরু করলেন, জীবন হঠাৎ করেই যেন তার কাছে মূল্যহীন এবং নেতিবাচক হয়ে পড়েছে। ঘটনাবলি তার জীবনকে অন্য এক স্তরে পৌঁছে দেয় যেখানে তার জীবন থেকে প্রতিদিনকার যাপনটি হারিয়ে যায়; জীবন হয়ে পড়ে বিষাদগ্রস্ত। যখন বুঝতে পারলেন যে তিনি আর জীবনের বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে নেই, তখন মারিয়া সারা-র সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লেন।
সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী: ‘দ্য হিস্ট্রি অব দ্য সিজ অব লিসবন’-এ রিমুন্দো ও মারিয়া উভয়কেই আগন্তুক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যারা তাদের নিজেদের শহরেই বহিরাগত। এমনকি নিজেদেরকে তারা ‘মুর’ বলেও পরিচয় দেয়।
সারামাগো: হ্যাঁ, তাই তো। তাই তো হবে। শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকেই আমরা তাদের মতো।
সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী: এখানে ‘আমরা’ দিয়ে কি পোর্তুগিজদের বোঝালেন?
সারামাগো: হ্যাঁ, তবে শুধুমাত্র পোর্তুগিজদের কথাই নয়… আমাদের সকলকেই শহরটিতে থাকতে হবে; আমি বোঝাতে চাইছি শহরটিকে সকলের সম্মিলিত বাসস্থান হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। কিন্তু একই সঙ্গে আমরা অবশ্যই শহরটিতে বহিরাগত, এবং মুর জাতির লোক; মুর আসলে এই অর্থে এখানে ব্যবহৃত হচ্ছে যে তারা এই শহরেরই আদিবাসী এবং একাধারে তারা পরদেশিও। তারা বহিরাগত হলেও পরিবর্তনকে প্রভাবিত করতে পেরেছে। মুর বংশীয়রা, অন্যরা, ভিনদেশিরা, এক একজন আশ্চর্য ভিনদেশি—আমরা বলব শহরের দেয়ালের ভিতরে থাকা সত্ত্বেও তার বাইরেই আছে। আমরা ইতিবাচক অর্থে ভাবতে পারি যে শহরটিকে তারা রূপান্তরিত করতে পারবে।
সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী: বিভিন্ন সময়ে আপনি পর্তুগাল সম্পর্কে নিজস্ব মতামত তুলে ধরেছেন। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশ হওয়ার পর পর্তুগাল সম্পর্কে কী ভাবছেন?
সারামাগো: এ সম্পর্কে উদাহরণ দিয়ে বলতে দিতে হবে। হুয়াও দুয়েস দে পিনহিয়ারো, যিনি ইউরোপীয় ইউনিয়নে পর্তুগালের কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত আছেন, এক সাক্ষাৎকারে জনৈক পোর্তুগিজ সাংবাদিক তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনার কি মনে হচ্ছে না যে জাতীয় ক্ষমতা কমে যাওয়া পর্তুগালের নিজের জন্য বিপজ্জনক ব্যাপার হবে? উত্তরে পিনহিয়ারো পালটা প্রশ্ন করেছিলেন সেই সাংবাদিককে, জাতীয় ক্ষমতা বলতে আপনি ঠিক কী বোঝাচ্ছেন? উনিশ শতকেও পোর্তুগিজ সরকার কোথাও নিজেদের একটি অফিস বসাতে পারেনি টেগাস নদীতে অবস্থানকারী ব্রিটিশ নৌবহরের এডমিরালের অনুমতি না পাওয়ায়। কথাগুলো বলেই তিনি হেসে উঠেছিলেন। কথা হল, ইউরোপীয় ইউনিয়নে প্রতিটি দেশের কমিশনার জরুরি যিনি বিশ্বাস করবেন এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পরবর্তীকালে পর্তুগাল জাতীয় ক্ষমতা ফিরে পায়নি। তারা নিজেরাই একদিন উপলব্ধি করল যে তারা তাদের জাতীয় ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, কারণ তারা বিশ্বাস করে ফেলেছিল যে কখনোই তাদের কোনো ক্ষমতা ছিল না।
ইউরোপীয় ইউনিয়ন যদি তার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারে তাহলে আমাদের রাজনীতিবিদদের দায়িত্ব অন্য দেশগুলোর রাজনীতিবিদদের মতই কমবে। আর তারা তাদের আসল চেহারায় ফিরে আসবে। রাজনীতিবিদ মানে-এজেন্ট। রাজনীতিবিদরা এখন নিছক এজেন্ট ছাড়া আর কিছু নয় কেন-না আমাদের সময়ের মহত্তম বিভ্রান্তি হচ্ছে গণতন্ত্র নিয়ে আলাপ, আলোচনা, বক্তৃতা। এই পৃথিবীতে গণতন্ত্র আর কাজ করছে না। গণতন্ত্রের পরিবর্তে কাজ করছে আন্তর্জাতিক অর্থনীতি। আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সাথে একাত্ম হয়ে রাজনীতিবিদরা বিশ্বকে শাসন করছে। রাজনীতিবিদরা প্রতিনিধি মাত্র—তথাকথিত রাজনৈতিক শক্তি ও অর্থনৈতিক শক্তির মধ্যে এটা একধরনের সম্পর্ক রক্ষার ধরন, যা সত্যিকারের গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত।
লোকে হয়তো জিজ্ঞেস করবে, আপনার বিকল্প প্রস্তাবগুলো কী? আমি বিকল্প কিছুর কথা বলব না। আমি তো নিতান্তই একজন ঔপন্যাসিক, আমি এই বিশ্ব সম্পর্কে তাই লিখি যেভাবে আমি তাকে দেখি। কিছু পরিবর্তন করা আমার কাজ নয়। আমি সবকিছুতে একা একা পরিবর্তন আনতে পারব না, এমনকি আমি এটাও জানি না যে কীভাবে পরিবর্তনটা সম্ভব। নিজের সমস্ত সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়েই আমি পৃথিবী সম্পর্কে ভাবিত হই।
কথা হল, আমি যদি কোনো প্রস্তাবনা রাখতে চাই তাহলে সেটা কী হবে। আমরা যাদেরকে পিছিয়ে পড়া বলে ধরে নিয়েছি তাদের জীবনমানের উন্নয়ন নিয়ে নানামুখি দ্বন্দ্ব তৈরি হয়ে থাকে। সকলেই চাইবে যারা উন্নয়নে এগিয়ে আছে তারা আরও উন্নতি করুক। পিছিয়ে পড়াদের উন্নয়নের মানেটা সাধারণ এবং সরল। যারা উচ্চমধ্যবিত্ত স্তরে আছে তারা স্বস্তিপূর্ণ জীবনযাপন করার সুযোগ পায়। উন্নয়নশীলতায় পিছিয়ে পড়াদের বলতে হবে, বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষ, তোমরা যারা পিছিয়ে পড়েছ, তোমরা নিজেরা নিজেদের এগিয়ে নাও। এবার ভাগ্য পরিবর্তন করো। কথাগুলো সবই ইউটোপিয়া। আমি ল্যানযেরোতেয় থাকি, জায়গাটি পঞ্চাশ হাজার জনসংখ্যা অধ্যুষিত একটি দ্বীপপুঞ্জ; এখানেই পঞ্চাশ হাজার! তাহলে সারা বিশ্বের বেলায় কী হবে। আমার উদ্দেশ্য কিন্তু পৃথিবীর উদ্ধারকর্তা হওয়া নয়। আমি তো এই সরল বিশ্বাসটি বুকে ধারণ করেই বেঁচে আছি যে, পৃথিবী আরও সুন্দর এবং বাসযোগ্য হতে পারত আর খুব সহজেই তাকে বাসযোগ্য এবং সুন্দর করে গড়ে তোলা যায়।
এই বিশ্বাসটি আমাকে দিয়ে বলাতে বাধ্য করে, যে পৃথিবীতে আমি আছি সেই পৃথিবীকে আমি পছন্দ করি না। দুনিয়া জোড়া বিপ্লব আমার কল্পনা। আমার এই ইউটোপীয় ভাবনাকে ক্ষমা করে দিলেই হয়তো আমি, আপনি এবং অন্যদের জন্য মঙ্গল হবে। আমরা দুজনেই যদি ঘুম ভেঙে জেগে উঠি এবং বলতে শুরু করি, আজকের দিনটিতে কাউকে নির্যাতন করব না; এভাবে যদি পরের দিনও আবার বলি আর প্রতিজ্ঞামতো চলতে থাকি, তাহলে পরিবর্তন আসতে খুব বেশি সময় লাগবে না। পৃথিবী বদলে যাবে আমূল। এটা আমার অর্থহীন ভাবনা—এরকম কখনোই ঘটবে না।
এইসমস্ত কারণগুলোই আমার ভেতর অবিরাম প্রশ্নের জন্ম দেয়। ‘অন্ধত্ব’ উপন্যাসটি লিখেছিলাম এই প্রশ্নগুলো মাথায় রেখেই। এসবই আমাকে সাহিত্যের কাজ করতে শক্তি জোগায়, বিষয়গুলোকে সাহিত্যের ভাষায় তুলে ধরি।
সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী: ‘অন্ধত্ব’-কে আপনি আপনার লেখা সবচেয়ে কঠিন উপন্যাস বলেছেন। একজন ব্যক্তি এবং তার অনুসারীদের নিষ্ঠুরতার কারণে প্রত্যেকেই সাদা অন্ধত্বের মহামারিতে আক্রান্ত। মানুষের আচরণগত এমন বিষয় নিয়ে কোনো কিছু লেখা অস্বস্তিকর। শেষ পর্যন্ত আপনি কি আশাবাদী?
সারামাগো: আমি হতাশাপ্রবণ লোক কিন্তু তাই বলে এত বেশি হতাশাগ্রস্ত না যে নিজেই নিজের খুলিতে গুলি করব। যে নিষ্ঠুরতার কথা আপনি তুললেন, তা শুধু উপন্যাসেই যে ঘটছে তা কিন্তু নয়, পৃথিবীর সব জায়গাতেই প্রতিদিন ঘটছে। আমরা এই তাৎপর্যময় মুহূর্তে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়া সাদা অন্ধত্বের শিকার। অন্ধত্ব এখানে ‘মেটাফর’। মেটাফর, কেন-না এই অন্ধত্ব মানুষের দ্বারা ছড়িয়ে পড়েছে। এই অন্ধত্বই আমাদেরকে কোনোরূপ বাধা না দিয়ে পাথরের গঠন সম্পর্কে পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য মঙ্গলে মহাকাশযান পাঠাবার ব্যবস্থা করেছে, একই সময়ে আমাদের গ্রহে অযুত নিযুত সংখ্যক মানুষ খাদ্যাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। আমরা হয় অন্ধ নয় উন্মাদ।
সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী: ‘দ্য স্টোন রাফ্ট’ও সামাজিক ইস্যুগুলো নিয়ে কথা বলেছে।
সারামাগো: আপনি যেভাবে বললেন আসলে পুরোটা তা নয় কিন্তু লোকে ব্যাপারটিকে এভাবেই দেখতে চেয়েছে। তারা ইউরোপ থেকে সমুদ্রবেষ্টিত আইবারিয়ান উপদ্বীপের পৃথকীকরণ হিসেবে এটাকে দেখতে পছন্দ করে। হ্যাঁ, তা তো অবশ্যই, এটা গল্পের একটা অংশ, এবং বাস্তবিক কী ঘটেছে—আইবারিয়ান উপদ্বীপ ইউরোপ থেকে নিজেকে পৃথক করেছে তারপর আটলান্টিক মহাসাগরে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু আমি যা বুঝতে পেরেছি তা কিন্তু ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্নতা নয়, কারণ এ থেকে কোনো কিছু নতুন করে পাওয়া হয় না। আমি যা বলতে চেয়েছিলাম এবং এখন যা বলতে যাচ্ছি তাকে আমি বাস্তব বলেই বিশ্বাস করি—পর্তুগাল ও স্পেনের শিকড় পুরোপুরি ইউরোপীয় নয়।
পাঠকদের আমি বলছি, শুনুন, আমরা সবসময় ইউরোপীয় ছিলাম, ইউরোপীয় আছি এবং ইউরোপীয়ই থাকব। অন্য কিছু হব না, কিন্তু আমাদের অন্য দায়িত্ব আছে, নৈতিক বাধ্যবাধকতা আছে, যেমন—ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত প্রকৃতির বাধ্যবাধকতা। আর তাই, আমরা নিজেদেরকে বাকি বিশ্ব থেকে আলাদা করব না; দক্ষিণ আমেরিকা থেকে নিজেদেরকে আলাদা করব না, আফ্রিকা থেকে আলাদা করব না। আমার এই ভাবনা কিন্তু কোনোভাবেই নয়া-ঔপনিবেশিক আকাঙ্ক্ষা নয়; কিন্তু আইবারিয়ান উপদ্বীপ, যাকে নিয়ে ‘দ্য স্টোন রাফ্ট’, যেখানে লাতিন আমেরিকা আর আফ্রিকাও ঢুকে পড়েছে, আর তার কারণও আছে। কারণ হচ্ছে, আমরা দক্ষিণ-দক্ষিণ-দক্ষিণ এবং দক্ষিণ বলতে বলতে পুরো জীবন কাটিয়ে দিচ্ছি। কারণ, দক্ষিণ সবসময়ই শোষণের জায়গা ছিল; আমরা তাই বলতে পারি, দক্ষিণও আমাদের কাছে উত্তরের দিকে নির্দেশিত হয়ে থাকে।
সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী: ‘ল্যানযেরোতে ডাইরি’ হচ্ছে আপনার শেষবারের নিউইয়র্ক ভ্রমণ নিয়ে লেখা, সেখানে আপনি বলেছেন ‘সে শহরে, ম্যানহাটনের উত্তরাঞ্চলই হচ্ছে দক্ষিণ’।
সারামাগো: হ্যাঁ, সেখানে দক্ষিণ নির্দেশিত হয় উত্তরে।
সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী: আপনাকে আমার বলতেই হবে ‘ল্যানযেরোতে ডাইরি’-তে চেলসি হোটেল সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছেন তা আমার অসাধারণ লেগেছে।
সারামাগো: সে এক ভীতিকর অভিজ্ঞতা! আমার প্রকাশকরাই সেখানে আমাকে পাঠিয়েছিলেন যদিও এখনও আমি জানতে পারিনি সেখানে যাওয়ার আসলে আইডিয়াটি কার ছিল। তারা মনে করেছিলেন আমিই সেখানে যেতে বলেছি কিন্তু আমি কখনোই কথাটা বলিনি, কাউকে। শহরের কোলাহলের বাইরে শান্ত সমাহিত হোটেল চেলসি, তা ঠিক আছে, কিন্তু আমি ভুলেও সেখানে যাওয়ার কথা বলিনি। থাকার ব্যবস্থা করতে বলিনি। আমার ধারণা তারা আমাকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন চেলসির ইতিহাসের জন্য, ইতিহাসের বহুকিছুই সেখানে আছে; কিন্তু আমি কি ‘ইতিহাস আছে’ এমন অস্বস্তিকর হোটেল বেছে নেব না কি ‘ইতিহাস নেই’ কিন্তু স্বস্তিকর—এমন জায়গায় যাব? নিজেকে ক্রমাগত এসব বলে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম; তবে, বলতেই হবে, এমন এক স্থান যে কোথাও আছে তা আমার ধারণারও বাইরের।
সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী: ইউরোপে, লাতিন আমেরিকায় আপনার প্রচুর পাঠক কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে সে তুলনায় যথেষ্ট কম।
সারামাগো: আমেরিকার পাঠকদের কাছে সিরিয়াস কোনোকিছু আবেদন তৈরি করতে পারে না, ব্যাপারটি অদ্ভুত। তবে, তারা যে রিভিউগুলো করে তা এক কথায় অসাধারণ।
সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী: সমালোচকদের সব কথাই কি আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ?
সারামাগো: আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কাজটিকে আমি ভালো করে করতে পেরেছি, অর্থাৎ, নিজের কাছে ভালো কাজের মানদণ্ড অনুযায়ী কাজটিকে ভালো কাজ বলে ধরে নিচ্ছি, বইটিকে আমি সেভাবেই লিখেছি যেভাবে লিখতে চেয়েছি। তারপর কাজটি শেষ, আমার ভেতর থেকে বের হয়ে গেছে। এখন সে পাঠকের। জন্মের পর জীবনের পথে হেঁটে যাওয়ার মতো বইটি তখন হাঁটবে। মা সন্তানের জন্ম দেন, তারপর সন্তানের জন্য সবসময় সবচেয়ে ভালো চিন্তাটিই করেন, কিন্তু জীবন? মা জন্ম দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু জীবনটা তো সন্তানের, সে তখন পথিক; সন্তানের জীবনটা তো আর মায়ের হবে না। সন্তান তার জীবনকে এখন নিজে নিজে এগিয়ে নেবে, নিজের জীবন নিজে গড়বে; তবে, অন্য কেউ জীবন গড়তে তাকে সাহায্য করতে পারে। মা তার জন্য যে স্বপ্নটি দেখেছিলেন হয়তো সেই স্বপ্নটি পূরণ হবে না। স্বপ্নটি বাস্তব হবে, এমন কোনো কথাও নেই। আমার বইয়ের জন্য আমার নিজের যে স্বপ্ন, যে উচ্ছ্বাস, পাঠকরা যাতে সংক্রমিত হবে বলে মনে করেছিলাম সেটা নাও হতে পারে, কেন-না পাঠকরা বই পড়ছে তাদের নিজেদের ইচ্ছায়, তাদের নিজেদের ধারণা থেকে।
আমি কখনোই বলব না যে আমার বইগুলোর লক্ষ্য থাকবে পাঠককে মুগ্ধ করা, কারণ পাঠককে মুগ্ধ করার অর্থ হল বইটির মান পাঠক সংখ্যার ওপর নির্ভর করছে। আমরা জানি যে এসব ব্যাপার মেকি এবং মিথ্যা।
সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী: যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণকালীন সময়ে আপনি ম্যাসাচুসেটসে, ফল নদীর কাছাকাছি একটি জায়গায় গিয়েছিলেন, সেখানে পোর্তুগিজদের একটা বেশ বড়ো কমিউনিটি আছে।
সারামাগো: হ্যাঁ, সেখানে কয়েকজন ইমিগ্রান্টের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম যারা আমার লেখাপত্রের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। অবাক হওয়ার বিষয় হল, আমার চারপাশে লোকের বেশ ভিড় ছিল, দিনগুলি কাটছিল কোলাহলমুখর পরিবেশের মধ্য দিয়ে, যদিও আমি তখন সাহিত্য নিয়ে কথা বলতে আগ্রহী ছিলাম না। আগ্রহটা একেবারে তলানিতে গিয়ে পৌঁছেছিল। আমি অনুমান করেছি যে, সাহিত্য নিয়ে কথা না বলার কারণে সেখানে বিরূপ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, কেন-না আমি তো বই লিখি, যদি সত্যিই বই লিখতে পারি তাহলে লেখালেখি ছাড়া আর কোনো বিষয় নিয়ে আমি কথা বলব না, শুধু লেখকের মতো লেখা নিয়ে কথা বলতে হবে। ভালো কথা যে আমি লিখি, কিন্তু লেখক হওয়ার আগে আমাকে তো এই জটিল পৃথিবীতে বাঁচতে হবে এবং অন্যরা যারা বেঁচে আছে তাদের সম্পর্কে জানতে হবে, বুঝতে হবে।
কয়েকমাস আগে আমি পর্তুগালের ব্রাগায় গিয়েছিলাম, সেখানে আমার সাহিত্যকর্মের ওপর একটি কনফারেন্স হয়েছিল; সেখানে আমরা বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেছি, কথা বলেছি পর্তুগালের সমগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে; আমাদের এখন কী করতে হবে—এসব নিয়ে। আমি বললাম, মানবজাতির ইতিহাসের দিকে তাকালে সেই ইতিহাসকে মনে হবে খুব জটিল, আসলে কিন্তু জটিল নয়, অত্যন্ত সরল, সাধারণ—আমরা একটি সংঘাতময় পৃথিবীতে বাস করছি।
 আমাদের টিকে থাকবার জন্যই সহিংসতা জরুরি। আমরা নিজ হাতে পশুপাখিদের হত্যা করব কিংবা আমাদের জন্য অন্যরা তাদের হত্যা করবে, কেন-না আমাদের জীবনধারণের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। গাছের ফলগুলোকে আমরা ডাল থেকে ছিঁড়ে নিলাম, এমনকি ফুলগুলোকেও আমাদের গৃহসজ্জার কাজে লাগাতে নিয়ে এলাম। সবগুলো কাজই অন্যান্য প্রাণির বিরুদ্ধে আমাদের সহিংসতার উদাহরণ। জন্তুদের স্বভাবও এরকম। মাকড়সা মাছিকে খাচ্ছে, মাছি খাচ্ছে অন্য কোনো উড়ুক্কু প্রাণকে। যাই হোক, মানুষ আর জন্তুদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো পার্থক্যটি হচ্ছে, জন্তুরা নিষ্ঠুর নয়। যখন একটি মাকড়সা তার বিস্তার করা জালে মাছিটিকে আটকে ফেলে, তার থেকে কিছুটা পরের দিন খাওয়ার জন্য সংরক্ষণ করে রাখে। শুনুন, মানুষই সংঘাত সহিংসতার কারিগর। বুদ্ধি ব্যবহার করে নির্দয় পদ্ধতিগুলো আবিষ্কার করেছে মানুষ। জন্তুজানোয়ারেরা একে অন্যকে নির্যাতন করে না কিন্তু আমরা করি। আমরাই মহাবিশ্বের একমাত্র হিংস্র প্রাণি।
আমাদের টিকে থাকবার জন্যই সহিংসতা জরুরি। আমরা নিজ হাতে পশুপাখিদের হত্যা করব কিংবা আমাদের জন্য অন্যরা তাদের হত্যা করবে, কেন-না আমাদের জীবনধারণের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। গাছের ফলগুলোকে আমরা ডাল থেকে ছিঁড়ে নিলাম, এমনকি ফুলগুলোকেও আমাদের গৃহসজ্জার কাজে লাগাতে নিয়ে এলাম। সবগুলো কাজই অন্যান্য প্রাণির বিরুদ্ধে আমাদের সহিংসতার উদাহরণ। জন্তুদের স্বভাবও এরকম। মাকড়সা মাছিকে খাচ্ছে, মাছি খাচ্ছে অন্য কোনো উড়ুক্কু প্রাণকে। যাই হোক, মানুষ আর জন্তুদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো পার্থক্যটি হচ্ছে, জন্তুরা নিষ্ঠুর নয়। যখন একটি মাকড়সা তার বিস্তার করা জালে মাছিটিকে আটকে ফেলে, তার থেকে কিছুটা পরের দিন খাওয়ার জন্য সংরক্ষণ করে রাখে। শুনুন, মানুষই সংঘাত সহিংসতার কারিগর। বুদ্ধি ব্যবহার করে নির্দয় পদ্ধতিগুলো আবিষ্কার করেছে মানুষ। জন্তুজানোয়ারেরা একে অন্যকে নির্যাতন করে না কিন্তু আমরা করি। আমরাই মহাবিশ্বের একমাত্র হিংস্র প্রাণি।
এই ব্যাপারগুলো আমার ভিতরে বেশ কিছু জিজ্ঞাসার জন্ম দেয়, জিজ্ঞাসাগুলো আমার স্থির বিশ্বাস যে অযৌক্তিক নয়। আমরা যদি হিংস্র হই তাহলে কীভাবে দিনের পর দিন নিজেদেরকে বোধসম্পন্ন প্রাণি মনে করি? কথা বলতে পারি বলে? চিন্তা করবার ক্ষমতা আছে বলে? সৃষ্টির সামর্থ্য আছে বলে? যদিও এসব আমরা করতে পারি তবুও তা যেন আমাদের সমস্ত নেতিবাচক এবং নিষ্ঠুর কাজ বন্ধের পক্ষে যথেষ্ট নয়। এগুলো আসলে নৈতিকতা সম্পর্কিত বিষয় যা নিয়ে আমাদের কথা বলতে হবে। আর এসব কারণেই সাহিত্য নিয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে আমার আগ্রহটা একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে।
মাঝে মাঝে আমি ভাবি, আমরা পৃথিবী গ্রহটি ছেড়ে আর কোথাও যেতে সমর্থ হব না, আর যদি যেতে পারি, মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ি, তবুও আমরা আমাদের আচরণে কোনো পরিবর্তন আনতে পারব না। সত্যি সত্যি যদি আমরা মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ি, আমরা যে তাতে সফল হব তা আমি বিশ্বাস করি না, তবে আমরা মহাবিশ্বকে আক্রান্ত করব। আমরা সম্ভবত এক বিশেষ ধরনের ভাইরাস যারা এই গ্রহে ভাগ্যক্রমে এসে পড়েছি। সম্প্রতি আমি আমাদের অস্তিত্বের ব্যাপারে আরও নিশ্চিত হয়েছি সুপারনোভার বিস্ফোরণ সম্পর্কে পড়ে। বিস্ফোরণের সেই আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছেছে তিন কি চার বছর আগে কিন্তু আসতে সময় লেগেছে একশ ছেষট্টি হাজার বছর। আমি ভাবলাম, ঠিক আছে, বিপদের কিছু নেই। মানুষ কখনোই এত দূর যেতে সক্ষম হবে না।