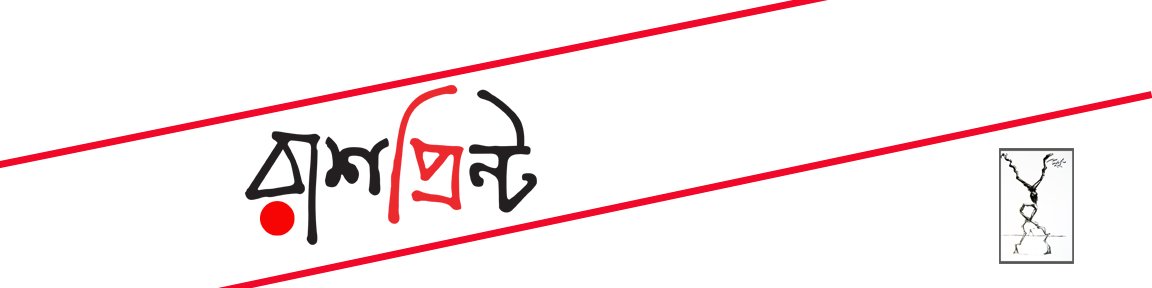স্মৃতিতে গিয়াসউদ্দিন আহমদ । সুমনকুমার দাশ
প্রকাশিত হয়েছে : ০৫ জুন ২০১৯, ১২:১২ অপরাহ্ণ, | ২০১৫ বার পঠিত

একটা ইয়াসিকা ক্যামেরা ছিল আমার। সহজলভ্য না-হওয়ায় তখন ব্যক্তিগত ক্যামেরা থাকাটা অনেকটা আভিজাত্যের লক্ষ্মণ বলেই কারও কারও কাছে মনে হতো। মূলত এই ক্যামেরার কারণেই সঞ্জয় নাথ সঞ্জু আমাকে সুরকার বিদিতলাল দাস প্রতিষ্ঠিত নীলম লোক সংগীতালয়ের একটি অনুষ্ঠানে নিয়ে গিয়েছিলেন। সিলেট নগরের শেখঘাট এলাকায় সংগীতালয়-সংলগ্ন ছোটো একটি মাঠে পয়লা বৈশাখের দিন আয়োজিত সে অনুষ্ঠানে সঞ্জুদাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল। আর সে সংবর্ধনাপ্রাপ্তির ছবি তুলতেই আমাকে সেখানে নেওয়া। তো, সে অনুষ্ঠানে গিয়ে আমি সামান্য একটু সময়ের জন্য বসেছিলাম সামনের সারিতে। তখন পাশের চেয়ারেই ছিলেন সিলেটের প্রখ্যাত গীতিকার গিয়াসউদ্দিন আহমদ। সফেদ লম্বা দাড়ি আর কাঁচাপাকা চুলে তাঁকে দারুণ দেখাচ্ছিল। এর আগে এক-দুইবার তাঁর সঙ্গে দেখা হলেও সেভাবে কখনও আলাপ-পরিচয় হয়নি। সেদিনই প্রথম আলাপ হলো। প্রথম আলাপেই জানিয়েছিলাম তাঁর লেখা কয়েকটি গান সম্পর্কে ব্যক্তিগত ভালো লাগার কথা। বিশেষত ‘মরিলে কান্দিস না আমার দায়’, ‘সিলেট পরথম আজান ধ্বনি বাবায় দিয়াছে’, ‘প্রাণ কান্দে মনো কান্দে রে কান্দে আমার হিয়া’, ‘হুরু ঠাকুর আমারে লইয়া সিলেট যাইবায়নি’, ‘বসন্ত আসিল গাছে ফুল ফুটিল’- এসব গানের কথা বলেছিলাম। শুনে তিনি মুচকি হেসেছিলেন। তিনিও সেখানে ওইদিন সম্মাননা পেয়েছিলেন। যতক্ষণ আমি তাঁর পাশে বসা ছিলাম, ততক্ষণ তাঁর সঙ্গে টুকটাক আরও কিছু আলাপ হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে, আমি কী করি, আমার বাড়ি কোথায়- এ-রকম এক-দুটি প্রশ্নও তিনি আমাকে করেছিলেন। সেদিনই ছিল তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও কী বুঝতে পেরেছিলাম, এটিই হবে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম এবং শেষ আলাপ। কারণ, সে অনুষ্ঠানের একদিন পরই তাঁর মৃত্যু হয়।
গিয়াসউদ্দিন আহমদ (১৯৩৫-২০০৫) মারা যান ২০০৫ সালের ১৬ এপ্রিল। এর পরের দিনের সংবাদপত্র পাঠে সে সংবাদ জানতে পারি। সম্ভবত ওই একই পত্রিকায় মৃত্যুর দু-দিন আগে পাওয়া তাঁর সম্মাননাপ্রাপ্তির খবরটিও ছাপা হয়েছিল। মৃত্যু আর সম্মাননালাভের অদ্ভুত এই যোগসূত্রের বিষয়টি ভাবতে গিয়ে আমি এখনও শিহরিত হই। আর ভাবি, যদি সঞ্জুদা সেদিন ওই অনুষ্ঠানে আমাকে না-নিতেন, তাহলে সিলেটের এই প্রখ্যাত গীতিকারের সঙ্গে সাক্ষাতের পুণ্যস্মৃতি অর্জন থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হতাম!
এরপর সময় আরও গড়ায়। একদিন গিয়াসউদ্দিন আহমদের গান বিশ্লেষণ করে একটি দীর্ঘ লেখা লিখি। সেটি দৈনিক ‘ইত্তেফাক’ পত্রিকার সাহিত্য সাময়িকীতে মুদ্রিত হয়। এর কিছুদিন পর ২০১১ সালের দিকে আমি ‘বাংলাদেশের বাউল-ফকির : পরিচিতি ও গান’ শীর্ষক একটি বই প্রকাশের উদ্যোগ নিই। সে বইয়ে গিয়াসউদ্দিন আহমদের কিছু গান সংকলনের জন্য প্রয়াত গীতিকবির ছেলে নাট্যসংগঠক মু. আনোয়ার হোসেন রনির সঙ্গে যোগাযোগ করি। এক রাতে সিলেট নগরের জিন্দাবাজার এলাকার রাজা ম্যানশনের সামনে দাঁড়িয়ে মুঠোফোনে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন আরেক নাট্যসংগঠক রজতকান্তি গুপ্ত। রনিভাই সানন্দে তাঁর বাবার গান নিয়ে কাজ করার অনুমতি দেন। ২০১২ সালে সে বইটি বের হয়েছিল। এরপর রনিভাইয়ের সঙ্গে টুকটাক আলাপ হলেও ঘনিষ্ঠতা সে অর্থে তৈরি হয়নি। পরে নাট্যসংগঠক হুমায়ূন কবীর জুয়েলের কাপড়ের দোকান ‘ষড়ঋতু’তে আড্ডা দেওয়ার সুবাদে রনিভাইয়ের সঙ্গে আমার চমৎকার এক সম্পর্ক তৈরি হয়। সে সম্পর্ক এখন পারিবারিক পর্যায়ে পৌঁছেছে। এখন তিনি আমার প্রিয় স্বজন, ঘনিষ্ঠজনদের একজন।
রনিভাই একসময় তাঁর বাবা গিয়াসউদ্দিন আহমদের রচনাসমগ্র প্রকাশের উদ্যোগ নেন। কবি আবিদ ফায়সাল দিনরাত পরিশ্রম করে পাণ্ডুলিপির প্রুফ সংশোধন করে দেন। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকালীন পরামর্শের পাশাপাশি চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি তৈরি হলে আমিও একনজর চোখ বুলিয়ে দিই। এরপর সম্পাদনাগত যাবতীয় কাজ শেষ করেন গবেষক মোস্তফা সেলিম। পরে যখন পাণ্ডুলিপিটি বই আকারে প্রকাশের জন্য প্রস্তুত, তখন রনিভাই আর আমি এক রাতে ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা দিই। মনে পড়ে, তখন নির্বাচন বর্জন করে এক অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করে রেখেছিল বিএনপি-জামায়াতের নেতৃত্বাধীন ২০-দলীয় জোট। সে অবস্থায় দূরপাল্লার গাড়ি চলাচল অনেকটা বন্ধ ছিল। দিনের বেলা কোনও যাত্রীবাহী বাস টার্মিনাল ছেড়ে যেত না, কেবল রাতে দু-একটা গাড়ি চলাচল করত! এ-রকম এক পরিস্থিতিতে অনেকটা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমরা কেবল গীতিসমগ্র প্রকাশের টানে ঢাকায় গিয়েছিলাম। এরপর সেলিমভাইয়ের সম্পাদনায় তাঁর প্রকাশনাসংস্থা উৎস প্রকাশন থেকে ২০১৫ সালের অমর একুশে বইমেলায় ‘গীতিসমগ্র’ বের হয়। এ সমগ্র প্রকাশকালীন কিছু স্মৃতিও রয়েছে। রনিভাই চেয়েছিলেন, সেলিমভাইসহ কয়েকজন লোকসংস্কৃতি গবেষকদের সমন্বয়ে একটি সম্পাদনা পর্ষদ গঠন করে বইটি প্রকাশিত হোক। সে পর্ষদে আমারও থাকার কথা ছিল! যদিও পরে রনিভাই, সেলিমভাই আর আমার মতামতের ভিত্তিতেই সে সিদ্ধান্তের বদল ঘটে।
এরপর কেটে যায় আরও কয়েক বছর। এই তো সেদিন গিয়াসউদ্দিন আহমদের ‘গীতিসমগ্র’-এর সম্পাদক মোস্তফা সেলিমভাই এলেন সিলেটে। তখন রনিভাই ভাবিকে নিয়ে সবেমাত্র সুন্দরবনসহ খুলনা অঞ্চল বেড়িয়ে এসেছেন। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন সেখানকার ঐতিহ্যবাহী খাবার চুঁইজাল। সে চুঁইজাল আর টার্কি মোরগের মাংস খেতে তিনি আমাদের আমন্ত্রণ জানান। তাঁর বাসায় গিয়ে সেদিন আমরা এক গল্পগুজবে মেতে উঠি। সেলিমভাই আর আমাকে পেয়ে রনিভাই তাঁর বাবার স্মৃতির যাবতীয় ঝাঁপি মেলে ধরেন। তিনি একের পর এক তাঁর বাবার গানের খাতা, স্বহস্তে লিখিত পাণ্ডুলিপি এবং ডায়েরির অংশবিশেষ দেখান। কোন গান কখন কোন জায়গায় লিখেছেন কিংবা সেসব গান প্রথম কোন শিল্পী গেয়েছেন, সেসবও তাঁর পাণ্ডুলিপিতে স্বাক্ষরসমেত উল্লেখ রয়েছে। এসব পাণ্ডুলিপি যখন নাড়াচড়া করছি, তখন রনিভাই একটি ডায়েরি আমাদের দেখান। মুহূর্তেই আমার চোখ সেখানে আটকে যায়। দেখি, গিয়াসউদ্দিন আহমদ সে ডায়েরিতে লিখেছেন তাঁর ছেলে জসীমউদ্দিনের টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে করুণ মৃত্যুর কাহিনি। তিনি লেখা শুরু করেছেন এভাবে- ‘স্বর্গীয় জসীমউদ্দিন। লিখক গিয়াসউদ্দিন আহমদ।’ ১৬ পৃষ্ঠা লেখা-সংবলিত ডায়েরি শেষ করেছেন- ‘ইয়া আল্লাহ্, তুমি আমার জসীমকে মহররমের চান্দের বরকতে কারবালার শহীদদানদের সঙ্গে শহীদি দরজা দ্বান করিও মাবুদ। আমিন।’ বাক্য দুটি দিয়ে। তাঁর দুঃখ-ভারাক্রান্ত বেদনার্ত হৃদয়ের উচ্চারিত পঙ্ক্তিগুলো পাঠে মনটা কেমন যেন খারাপ হয়ে পড়ে। তখনই চোখে পড়ে তাঁর পাণ্ডুলিপিতে থাকা ‘মরিলে কান্দিস না আমার দায়’ গানটি। গানের নিচে লেখা রয়েছে রচনার সাল ও তারিখ। সে তথ্যানুযায়ী, এ গানটি তিনি ১৯৭৪ সালের ৪ নভেম্বর সকাল ১০টা ৫ মিনিটে রচনা করেছেন। সেখানে শিল্পী সুরুজ মিয়া গানটি গেয়েছেন বলে উল্লেখ করা। এরপর বিদিতলাল দাস টেলিভিশনে গানটি গেয়েছেন বলেও লেখা রয়েছে। পাণ্ডুলিপিতে উল্লেখ না-থাকলেও তাঁর বেশিরভাগ গানের মতোই এ গানটিরও সুরকার বিদিতলাল দাস (১৯৩৮-২০১২)।
‘মরিলে কান্দিস না আমার দায়’ গানটির আলোচনা-প্রসঙ্গেই মনে পড়ে প্রয়াত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২)-এর কথা। কারণ, তিনি এ গানটি অত্যন্ত পছন্দ করতেন। প্রায়ই তিনি এ গান শুনতেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগেও হুমায়ূন তাঁর স্ত্রী মেহের আফরোজ শাওনকে দিয়ে সুদূর বিদেশ-ভুঁইয়ে নিউইয়র্কে বসে বাদ্যযন্ত্রহীন কণ্ঠে গানটি গাইতে অনুরোধ করেছিলেন। স্বামীর অনুরোধ রক্ষা করতে গিয়ে শাওন অত্যন্ত দরদ দিয়ে গানটি গেয়েছিলেন, আর চোখ মুদে মাথা দুলিয়ে সে গান শুনছিলেন আর কাঁদছিলেন হুমায়ূন- যে দৃশ্যের একটি ভিডিও ইউটিউবে ব্যাপক ভাইরাল হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, এরও আগে হুমায়ূন ২০০২ সালে তাঁর হিমুবিষয়ক সিরিজের ‘চলে যায় বসন্তের দিন’ শীর্ষক উপন্যাসের উৎসর্গলিপিতে ‘মরিলে কান্দিস না আমার দায়’ গানটিকে ‘মরণ-সংগীত’ অভিধায় চিহ্নিত করেছিলেন। এমনকী হুমায়ূন তাঁর মৃতদেহের পাশে বসে স্বজনদের এ গানটি গাওয়ার অসিয়ত করেছিলেন। হুমায়ূন মারা যাওয়ার পর বাংলাদেশের জনপ্রিয় দৈনিক ‘প্রথম আলো’ তাঁর মৃত্যুসংবাদ লিখতে আট কলাম জুড়ে গিয়াসউদ্দিন রচিত গানের পঙ্ক্তি ‘মরিলে কান্দিস না আমার দায়’ বাক্যটিই ব্যবহার করেছে। গ্রামীণ এক গীতিকবির পঙ্ক্তি ব্যবহার করে প্রধান শিরোনাম করার এমন বিষয়টি যেমন অভিনব, তেমনই এটি অজপাড়াগাঁয়ের এক কবির সৃষ্টির প্রতিও এক ধরনের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন।
সেই শ্রদ্ধা হুমায়ূন আহমেদও জীবদ্দশায় একাধিকবার করেছিলেন। তিনি নানা সময়ে আলাপচারিতায় এ গানটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সূত্রে একটি অনুষ্ঠানের গল্প বলা যেতে পারে। ২০০৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর সিলেটের রিকাবিবাজার এলাকার তৎকালীন এম. সাইফুর রহমান মিলনায়তনে (বর্তমানে কবি নজরুল অডিটোরিয়াম) গিয়াসউদ্দিন আহমদের ‘শেষ বিয়ার সানাই’ (২০০৫) গীতিসংকলনের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে হুমায়ূন আহমেদ প্রধান অতিথির বক্তব্য দিয়েছিলেন। সে অনুষ্ঠানে আবেগমিশ্রিত কণ্ঠে হুমায়ূন বলেন, “সময় আসবে। আমি মারা যাব। আমার পরিবারের সবাইকে বলে রেখেছি, আমি মারা যাওয়ার পরপরই কোরান শরিফ, সুরা ইউনুসের আগেও যেন বাজানো হয় ‘মরিলে কান্দিস না আমার দায়’ গানটি। আমার ঘরোয়া সব অনুষ্ঠান শুরু হয় হাসন রাজার ‘বাউলা কে বানাইল রে’ গানটি দিয়ে আর শেষ হয় ‘মরিলে কান্দিস না আমার দায়’ গানটি দিয়ে। এই গানটি শোনার সময় আমার মধ্যে একটা অদ্ভুত ঘোর তৈরি হয়। গানটি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার এবং আমার অনেক বন্ধুর চোখ ভিজে উঠে জলে।”
সেদিনের ওই প্রকাশনা অনুষ্ঠান উপলক্ষে ‘কান্দে আমার হিয়া’ নামের একটি পুস্তিকা বের হয়েছিল। আবুল ফতেহ ফাত্তাহ সম্পাদিত ওই পুস্তিকায় গিয়াসউদ্দিন আহমদের একটি ছোটো সাক্ষাৎকার মুদ্রিত হয়েছে। এটি গ্রহণ করেছিলেন আমিনুল ইসলাম চৌধুরী। আবিদ ফায়সাল অনুলিখিত ওই সাক্ষাৎকারের একটি অংশে ‘মরিলে কান্দিস না আমার দায় গান প্রসঙ্গে গিয়াসউদ্দিন বলেছিলেন- “এই পৃথিবীতে যেদিন আমি থাকব না, একজন আমার জন্য কাঁদল। আমি তার কান্নাটা দেখলাম না বা তার কাঁদন শুনলাম না। আমার ইচ্ছেটা এই আমার জন্য যা করা হলো তা যদি দেখলাম না, সেটা না করাই ভালো; যেটা আমি পাই সেটা করাই ভালো, উত্তম। গানেই তো আছে ‘সুরে ইয়াসিন পাঠ করিও বসিয়া কাছায়, আমার প্রাণ যাবার বেলায়।’ কান্নার চেয়ে সেটাই ভালো। আমি পাব। আল্লার নাজাতই আমি চাই। কান্নার চেয়ে দোয়া ভালো। দোয়াই দরকার।” প্রসঙ্গক্রমেই বিদিতলাল দাসের একটি স্মৃতিচারণার প্রসঙ্গ মনে পড়ে। এটি মুদ্রিত হয়েছিল বিদিতলালের ‘সুরমাপারের গান’ বইয়ে। সেখানে মঈন উদ্দিন মন্জু ‘শেষ বিয়ার সানাই’ গ্রন্থের প্রকাশনা-উৎসব নিয়ে লিখতে গিয়ে বিদিতলাল দাসের বরাতে বলেছেন- “শেষ বিয়ার সানাই ছিল গিয়াসউদ্দিন আহমদের শেষ গান। এ সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে গীতিকার গিয়াসউদ্দিন আহমদের অধিকাংশ গানের সুরকার বিদিতলাল দাস বলেন, মৃত্যুর ঠিক আগের রাতে গিয়াসউদ্দিন ‘শেষ বিয়ার সানাই’ গানটি আমার হাতে দিয়ে বলেন, গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে এ গান গাইতে হবে। এরপর তিনি চলে যান। রাত তখন ১টা। আমি কাগজটি না-পড়ে পাঞ্জাবির পকেটে রেখে ঘুমিয়ে পড়ি। সকালে বেতারের এক কর্মকর্তা ফোন করে জানান, গিয়াসউদ্দিন আহমদ আর আমাদের মাঝে নেই। সঙ্গে সঙ্গে আমি পাঞ্জাবির পকেট থেকে কাগজটি পড়ে দেখতে পাই ‘শেষ বিয়ার সানাই’ গানের সঙ্গে তার মৃত্যুর অদ্ভুত মিল রয়েছে।”
সেই প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বিদিতলাল দাস মাত্রই কয়েক মাস আগে প্রয়াত তাঁর প্রিয় বন্ধু গিয়াসউদ্দিন আহমদের লেখা ‘শেষ বিয়ার সানাই’ গানটি গেয়েছিলেন। মিলনায়তন-ভরতি মানুষ ছিলেন, তবে ছিল পিনপিতন নীরবতা। সে নীরবতা ভেদ করে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বিদিতলাল অনুষ্ঠানের সেই রাতে আবেগী কণ্ঠে গেয়ে উঠেছিলেন—
শেষ বিয়ার সানাই বাজিল, ডাকছে কাল শমনে
আমার বাসরঘর হবে গো
সাড়ে তিন হাত মাটির ঘরে প্রাণবন্ধুর সনে ॥
গরম জলে সাবান গুলে গোসলও করাইও
কর্পূর গুলিয়া সারা অঙ্গে মাখাইও
আতর গোলাপ ছিটাইও অঙ্গের বসনে ॥
সাদা কাপড় দিয়া বিয়ার সাজন সাজাইবা
প্রাণবন্ধুর নামটি আমার বুকে লিখিবা
কুহেতুরের সুরমা দিবা আমার দুই নয়নে ॥
বাঁশের পালকি সাজাইয়া কান্ধে উঠাইয়া
শব মিছিল করিও সবে কলিমা পড়িয়া
মাটির ঘরে রাইখ নিয়া পরম যতনে ॥
আন্ধার ঘরে গিয়াস পাগল নাই রে ভাবনা তোর
বন্ধুর রূপে হইবে আলো সেই না বাসরঘর
জীবনের সাধ মিটবে রে তোর বন্ধু দরশনে ॥