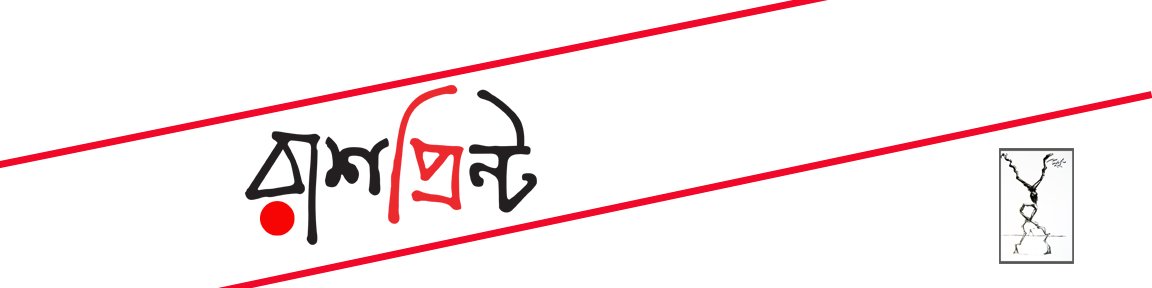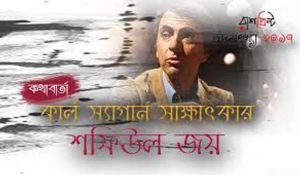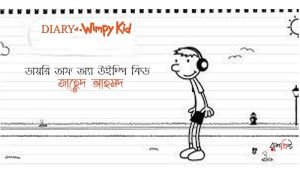পিঙ্ক ফ্লয়েড ইন্সাইড আউট । শফিউল জয়
প্রকাশিত হয়েছে : ২০ জুলাই ২০১৬, ২:২১ অপরাহ্ণ, | ৪০২২ বার পঠিত
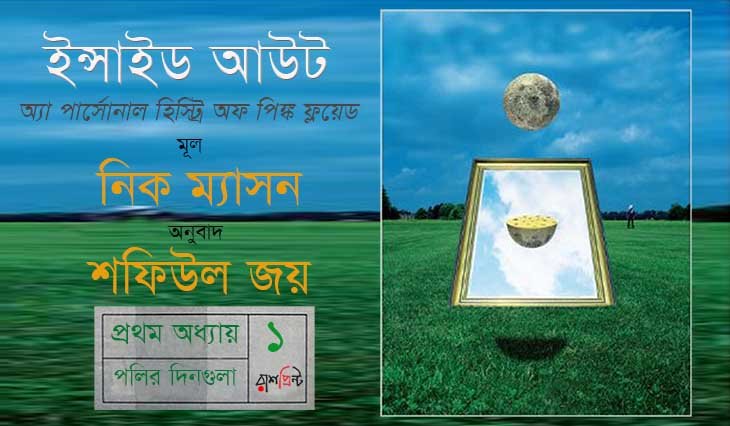
কলেজে সেরা ছয় মাস একসাথে কাটানোর পর রজার ওয়াটার্স আমার সাথে প্রথম কথা বলার তাগাদা অনুভব করছিল। টেক্নিক্যাল ড্রয়িঙে মনোযোগ দেয়ার জন্যে একদিন বিকালে আমি যখন চল্লিশজন আর্কিটেকচারের বন্ধুবান্ধবদের হাল্কা ঝাড়ি মাইরা থামানোর চেষ্টা করতেছিলাম, সেই সময় রজারের লম্বা, পরিচিত ছায়া হুট করে আড়াআড়িভাবে আমার ড্রয়িংবোর্ডের উপরে আইসা পড়লো। সচরাচর ও আমার উপস্থিতি ইচ্ছাকৃতভাবেই এড়ায়া যাওয়ার চেষ্টা করত, তারপর একসময় বুঝতে পারল আমি আসলে সম্ভাবনাময় স্থপতির শরীরের মধ্যে আটকা-পড়া একজন অমায়িক সংগীতময় আত্মা। কন্যা আর কুম্ভরাশির জ্যোতিষ্ক আমাদের অনাগত লক্ষ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে রজারকে উদ্বুদ্ধ করছিল দুইজনের মনকে একত্রে একটা মহান সৃষ্টিশীল উত্তেজনার রাস্তা বাইছা নিতে।
না না। এত বাড়ায়া বলাটা ঠিক হইতেছে না। রজার আমার সাথে কথা বলার আগ্রহ দেখাইছিল তার একমাত্র কারণ — আমি যাতে আমার গাড়িটা তারে ধার দেই।
যে গাড়িটার কথা বলা হইতেছে সেটা আমি পাইছিলাম বিশ কুইডে — একটা ১৯৩০ অস্টিন সেভেন ‘চামি’। ওই সময়ের পোলাপানরা হয়তো আরেকটু ভালো দেইখা মরিস ১০০০ ট্রাভেলার কেনার কথা চিন্তা করত। কিন্তু আব্বা আগে থেকেই পুরানা গাড়ির প্রতি এক-ধরনের টান তৈরি করে দিছিল এবং তার ফলস্বরূপ এই গাড়ি পাইছিলাম। আব্বার তদারকিতেই গাড়িটা ঠিকঠাক রাখার চেষ্টা করতাম। যা-ই হোক, রজারের মনে হয় আমার গাড়িটা ধার করা খুব দরকার ছিল। কারণ এই গাড়িটা এত্ত হেইলা-দুইলা চলত যে তা আর বলার মতো না। একবার খুব লজ্জায় পইড়া এক হিচহাইকারকে গাড়িতে উঠাইতে বাধ্য হইছিলাম। তার পাশে দিয়া গাড়ি নিয়া এত্ত আস্তে আস্তে যাইতেছিলাম যে সে মনে করছিল লিফ্ট দেয়ার জন্যেই আমি স্পিড কমায়া পাশ ঘেইষা আগাইতেছি। রজারকে জানাইলাম একটু ঝামেলা আছে কাগজপত্রের, অবশ্য কথাটা পুরাপুরি সত্য তা-ও না। ধার দেয়াটা আমার ভেতর থেকে সায় দিতেছিল না, কিন্তু ওকে দেইখা একটু ভয়ও লাগত। কিছুদিন পরে ও যখন অস্টিনটা চালাইতে দেখছে, আমার ভেতরের দ্বিচারিতা আর কূটনামির মাঝখানের নোম্যান্স ল্যান্ড দখলের ঝোঁকটা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারছিল। তার আগে একদিন দেখছিলাম আমাদের ক্লাসের রিক রাইটকে খুব ঝাড়ি মারতেছে। সিগারেট চাইছিল ওর কাছে, রিক সাথে সাথে না করে দিছিল যে দিব না। এটা ছিল রিকের সুপরিচিত দয়াশীলতার প্রথমদিককার উদাহরণ। উন্নিশশো তেষট্টির এই একঘেয়ে টুকটাক পরিচয়গুলাই ছিল পরবর্তীকালে একসাথে অনেক বছর কাটানো নির্বিঘ্ন দিনগুলোর বীজক্ষেত্র।
পিঙ্ক ফ্লয়েডের জন্ম হইছিল দুইটা বন্ধুসার্কেলের একসাথে মিলায়া যাওয়ার মধ্য দিয়া। একটা ছিল কেম্ব্রিজের আশেপাশের — যেইখান থেকে রজার, সিড ব্যারেট, ডেভিড গিল্মোর আর ভবিষ্যতের অনেক ফ্লয়েডিয়ানরা আসছিল। অন্যদিকে রজার, রিক আর আমি পরিচিত হইছিলাম লন্ডনের রিজেন্ট স্ট্রিট পলিটেক্নিকের প্রথম বছরের কোর্সের মাধ্যমে। আমাদের এই বইটার কাহিনি শুরু ওইখান থেকেই।
 সত্যি কথা বলতে পলিতে ঢোকার আগে (এখন যার নাম য়্যুনিভার্সিটি অফ ওয়েস্টমিনিস্টার) আমি ড্রামার হিশাবে একবার অবসরও নিয়ে নিছিলাম এর মধ্যে। সেই সময় কলেজটা ছিল লিটল টিচফিল্ড স্ট্রিটে, অক্সফোর্ড স্ট্রিটের ওয়েস্ট এন্ডের কাছাকাছিই। এক বিশাল হিতবাদী পাব্লিক স্কুলের স্মৃতিবহ পলির পুরান ধাঁচের কাঠের কারুকার্য দেইখা মনে হতো বহুকাল আগে থেকে এর উপস্থিতি। যতদূর মনে পড়ে চা বানানোর জিনিশপত্র ছাড়া সেখানে তেমন কোনো সুযোগসুবিধা ছিল না। কিন্তু টিচফিল্ড আর পোর্টল্যান্ড স্ট্রিটের কাপড়ের ব্যবসার মধ্যখানে থাকার জন্যে নানাধরনের ক্যাফের উপস্থিতি ছিল। ওইখানে দুপুর পর্যন্ত ডিম, সসেজ আর চিপ্স পাওয়া যাইত। স্টেক, কিডনি-পাই আর রলি-পলির তো ছিল লা-জওয়াব।
সত্যি কথা বলতে পলিতে ঢোকার আগে (এখন যার নাম য়্যুনিভার্সিটি অফ ওয়েস্টমিনিস্টার) আমি ড্রামার হিশাবে একবার অবসরও নিয়ে নিছিলাম এর মধ্যে। সেই সময় কলেজটা ছিল লিটল টিচফিল্ড স্ট্রিটে, অক্সফোর্ড স্ট্রিটের ওয়েস্ট এন্ডের কাছাকাছিই। এক বিশাল হিতবাদী পাব্লিক স্কুলের স্মৃতিবহ পলির পুরান ধাঁচের কাঠের কারুকার্য দেইখা মনে হতো বহুকাল আগে থেকে এর উপস্থিতি। যতদূর মনে পড়ে চা বানানোর জিনিশপত্র ছাড়া সেখানে তেমন কোনো সুযোগসুবিধা ছিল না। কিন্তু টিচফিল্ড আর পোর্টল্যান্ড স্ট্রিটের কাপড়ের ব্যবসার মধ্যখানে থাকার জন্যে নানাধরনের ক্যাফের উপস্থিতি ছিল। ওইখানে দুপুর পর্যন্ত ডিম, সসেজ আর চিপ্স পাওয়া যাইত। স্টেক, কিডনি-পাই আর রলি-পলির তো ছিল লা-জওয়াব।
আর্কিটেকচার স্কুলটা ছিল কয়েকটা একই ধরনের অন্যান্য বিষয়ের বিল্ডিঙের ভিতরেই। পলি বেশ প্রশংসিত প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠছিল এর মধ্যেই, যদিও খুব পুরানো কায়দায় পড়াশোনা করানো হতো। যেমন বলা যায়, স্থাপত্যের ইতিহাস কোর্সে একজন লেকচারার আসতো খুব গম্ভীর ভাব নিয়ে। তারপর বোর্ডে নিখুঁতভাবে কর্নকের খনের মন্দির আইকা আমাদের বলত খাতায় কপি করতে। একইভাবে তিরিশটা বছর ধরে এই নিয়ম চলতেছিল। যা-ই হোক, পুরানো চর্চা ভেঙে স্কুলটা তাদের লেকচার সিস্টেমে পরিবর্তন আনতেছিল। নতুন চিন্তাভাবনা করতেছে এ-রকম বিশিষ্ট স্থপতিদের প্রায়ই আমন্ত্রণ জানানো হতো। এই তালিকায় ছিল এল্ড্রেড ইভান্স, নর্মান ফস্টার এবং রিচার্ড রজারের মতো স্থপতিরা। ফর্মের দিক থেকে বিচার করলে ফ্যাকাল্টিরা ছিল সিদ্ধহস্ত।
কোনো বড় লক্ষ্য নিয়ে আর্কিটেকচার পড়তে গেছিলাম এমনটা বলা যায় না। এটা সত্য যে আর্কিটেকচার নিয়ে আগ্রহ ছিল, কিন্তু এই বিষয়েই ক্যারিয়ার করতে হবে এমন কোনো চিন্তা তখনো করি নাই। মনে করছিলাম আর্কিটেক্ট হই আর অন্য যা-ই হই না কেন — টাকা কামানোর জন্যে কোনোটারই খুব-একটা পার্থক্য নাই। কিন্তু তখন যে মিউজিক নিয়াও খুব ভাবতাম, স্বপ্ন দেখতাম তা-ও না। ড্রাইভিং লাইসেন্সের আগমন বয়ঃসন্ধির ওই সময়টার বাকিসব চিন্তাভাবনাকে ঢাইকা রাখছিল।
আমার তেমন কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না; তবে কোর্সটা কলা, গ্রাফিক্স আর প্রযুক্তির মিশেলে একটা সামগ্রিক ধারণা দেয়ার চেষ্টা করত। রজার, রিক আর আমি কমবেশি প্রযুক্তি আর ভিজুয়াল ইফেক্টের সম্ভাবনা আর সীমানার নানা দিক নিয়ে আগ্রহী হইছিলাম। পরের বছরগুলাতে আলোস্তম্ভ থেকে শুরু করে অ্যালবাম কাভার আর্টওয়ার্ক, স্টুডিও, স্টেইজ সাজানো সবকিছু করার সাথেই আমাদের ব্যাপক সম্পৃক্ততার কারণও কিছুটা এটাই। আর্কিটেকচারের দীক্ষা দক্ষ কারিগরদের সাথে একটা ভালো বোঝাপড়া তৈরি ও মতামত বিনিময়ের ক্ষেত্রে সাহায্য করছিল।
যারা আরেকটু সূক্ষ্মভাবে জানতে চান, তাদের বলি — প্রযুক্তি আর ভিজুয়ালের মিশ্রণের টেক্নিক নিয়া আগ্রহটা আসছিল আব্বার কাছ থেকে। আব্বার নাম ছিল বিল, পেশায় তখন ডকুমেন্টারি ডিরেক্টর। আমার বয়স যখন দুই, আব্বা তখন শেল ফিল্ম ইউনিটে চাকরি পায়। ফলে যেখানে আমার জন্ম — বার্মিংহামের এজবাস্টন মফস্বল থেকে উত্তর লন্ডনে আইসা পড়ি। আমার প্রাথমিক জীবনও কাটে ওইখানেই।
যদিও আব্বা গানের মধ্যে ছিল না, কিন্তু গানটান নিয়ে খুব উৎসাহী বলতে যা বোঝায় সে ছিল তা-ই। বিশেষ করে তার ফিল্মের মিউজিক নিয়ে। ফিল্ম বানানোর সেইসব মুহূর্তগুলাতে আব্বা জ্যামাইকান স্টিল ব্যান্ড থেকে শুরু করে অপেরার স্ট্রিং সেকশন, জ্যাজ কিংবা রন গেসিনের উদ্দাম আর বুনো ইলেক্ট্রিক বাজনা সবকিছু নিয়াই তুমুল আগ্রহ দেখাইত। রেকর্ডিঙের যন্ত্রপাতি, স্টেরিও টেস্ট রেকর্ড, সাউন্ড, সাউন্ড-ইফেক্ট আর রেসিং কার — সবকিছু নিয়েই সে ছিল অত্যুৎসাহী। স্বভাবগুলা পরে আমিও পাইছি।
যা-ই হোক, পরিবারের ভেতরেই মিউজিক করার চল আগে থেকে কিছুটা খুঁজে পাওয়া যায়। আমার দাদা ওয়াল্টার কার্শ্যো তার চার ভাইয়ের সাথে একটা ব্যাঞ্জো ব্যান্ডে বাজাইতেন এবং ‘দ্যা গ্র্যান্ড স্টেইট মার্চ’ নামের একটা মিউজিকও প্রকাশিত হইছিল তার। স্যলি — আমার মা-ও ছিল একজন দক্ষ পিয়ানিস্ট। তার তোলার মধ্যে ডেবুসির গলিউগ’স্ কেকওয়াক-ও ছিল। ডেবুসিরটা যদিও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এখন চরম ত্রুটিপূর্ণ। বাসার বহুবিধ ও বিচিত্র গ্রামোফোনরেকর্ডগুলার মধ্যে ছিল রেড আর্মির ‘কমিউনিস্ট শ্রমিকের গান’, ‘টেডি বিয়ার পিক্নিক’, ‘লাফিং পুলিসম্যান’। সন্দেহ নাই আমাদের গানের মধ্যে এগুলার প্রভাবগুলো হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে, কিন্তু অন্য কারো জন্যেই সেটা তোলা থাকল বের করার। পিয়ানো, ভায়োলিন দুইটাই কিছুদূর শিখছিলাম, কিন্তু আমার মিউজিক-প্রতিভা যেহেতু এই বাদ্যযন্ত্রগুলা বের করে আনতে পারে নাই — ফলত খুব তাড়াতাড়িই বাতিলের খাতায় চলে যায় এই দুইটা ইন্সট্রুমেন্টের নাম।

আমার দাদা কার্শ্যোর ব্যাঞ্জো ব্যান্ড, প্রথম সারির দ্বিতীয়জন
আমি এটাও স্বীকার করব ব্রিটেনে ১৯৫৬ সালে রিলিজ্-পাওয়া ফেস পার্কারের ‘দ্যা ব্যালাড অফ ডেভি ক্রকেট’ সিঙ্গেলের প্রতিও টান ছিল। মিউজিকের সাথে মার্চেন্ডাইজিঙের অপবিত্র সম্পর্ক যে তখনও বিদ্যমান, তার প্রমাণ তখন রেকুনের চামড়ার একটা ক্যাপ পইরা ঘুরতাম। ক্যাপটা স্পেশালি লেজের অংশ দিয়ে বানানো ছিল।
সম্ভবত বারো বছর বয়সে রক্ মিউজিক জিনিশটার অস্তিত্ব আমার মাথায় প্রথমবারের মতো ঢোকে। মনে পড়ে হোরেস ব্যাচেলরের অদ্ভুত ধরনের পুল সিস্টেমের কথা শুনতে শুনতে খুব কষ্ট করে জাইগা থাইকা, রেডিও লুক্সেমবার্গের ‘রকিং টু ড্রিমল্যান্ড’ ধরার চেষ্টা করতেছি রেডিওতে। বিল্ হ্যালি-কে টপচার্টে উঠানোর জন্য পরোক্ষভাবে সাহায্য করছিলাম স্থানীয় দোকান তার ‘সি ইউ লেটার অ্যালিগেটর’-এর গ্রামোফোন রেকর্ড কিনে — যেটা ইউকে টপ টেনে উঠছিল ১৯৫৬ সালে। সেই বছরের শেষদিকে এলভিস প্রিসলির ‘ডোন্ট বি ক্রুয়েল’-ও কিনছিলাম। এইগুলা বাজানো হতো আমাদের বাসার লেটেস্ট মডলের গ্রামোফোনে। ইলেক্ট্রিক এই গ্রামোফোনটা একটা ডিভাইসের সাথে লাগানো ছিল যেটারে দেইখা মনে হতো ফ্রান্সের রাজা লুই চইদ্দোর আমলে বানানো একটা ক্যাবিনেট আর রোল্স রয়েসের ড্যাশবোর্ডের মাঝামাঝি কিছু একটা। তেরোতে আমার প্রথম লং-প্লেয়িং অ্যালবাম পাইছিলাম — এলভিসের ‘রক্ অ্যান্ড রল্’। এই স্মরণীয় অ্যালবামটা পিঙ্ক ফ্লয়েডের অন্তত আরও দুইজন সদস্যের কেনা প্রথম এলপি রেকর্ড, এবং সম্ভবত আমাদের প্রজন্মের প্রায় সব রক্ মিউজিশিয়ানের ক্ষেত্রেই কমবেশি কথাটা সত্য। শুধুমাত্র মিউজিকের জন্যে না — অ্যালবামটায় অন্যরকমের এক-ধরনের পোলাপাইন্যা বিদ্রোহ ছিল। এই অ্যালবাম শুনতে গেলে বাপ-মার কাছ থেকে এক-ধরনের প্রতিক্রিয়া পাইতাম, যেমনটা তারা দেখাইত আমাদের পোষা মাকড়শার প্রতি।
এটা ছিল সেই সময় যখন আমি আমার ব্যাগ নিয়ে, ফ্লানেলের ট্রাউজার, গোলাপীর মধ্যে কালো ট্রিম আর আয়রন ক্রস ব্যাজ লাগানো স্কুলব্লেজার পরে পূর্ব লন্ডনের বিভিন্ন ভেন্যুতে টমি স্টিলের শো দেখে বেড়াইতেছি। একা একাই ঘুরতাম মূলত, আমার কোনো বন্ধুবান্ধবেরই বলতে গেলে এসব নিয়া আগ্রহ ছিল না। টমি ছিল বিলবোর্ডে এক নাম্বারে, আর বাকিদের অবস্থা ছিল আশঙ্কাজনক। কমিক্স, জাদুকর আর ইংলিশ মিউজিক হলের বাকি উদ্বাস্তুরা সবাই হুড়াহুড়ি করে হল্ খালি করে দিত টমি আসার আগেই, কিন্তু আমি থাকতাম। আমার কাছে তাকে চরম লাগত। সে যখন ‘সিংগিং দ্যা ব্লুজ’ আর ‘রক্ উইথ দ্যা কেইভম্যান’ গাইত, আমি হা হয়া তাকায়া থাকতাম। কারণ ঠিক এইভাবেই তখনকার ইউকে টেলিভিশনের বিখ্যাত পপ-শো ‘দ্যা সিক্স ফাইভ স্পেশাল’-এ গাওয়া হইত। সে এলভিস ছিল না, কিন্তু আমার আয়ত্তের মধ্যে প্রায় এলভিসের কাছাকাছি ভালো অন্তত।
কয়েক বছরের মধ্যেই আমার আশেপাশে এমন কয়েকজন বন্ধুবান্ধব পেয়ে গেলাম যারা রক্ অ্যান্ড রল্ সম্পর্কে জানে। আমার মনে হইল একটা ব্যান্ড করলে মন্দ হয় না। আমরা কেউই জানতাম না কীভাবে বাজাইতে হয়, কিন্তু এটা কোনো সমস্যাই হয়ে উঠতে পারে নাই, কারণ আমাদের কোনো ইন্সট্রুমেন্টই ছিল না। কে কী বাজাবে সেটা ঠিক করা হইছিল অনেকটা লটারির মতো করে। আব্বা আর মা-র একজন সাংবাদিক বন্ধু ছিলেন ওয়েন্ মিনোউ নামের, যে আমাকে একজোড়া ওয়্যার ব্রাশ দিছিলেন। ড্রামের সাথে আমার সংযোগ ছিল মোটের উপরে এই। পিয়ানো আর ভায়োলিন শেখার ব্যর্থতার পর মনে হইল আমার আসলে ড্রামারই হওয়া উচিত। প্রথম ড্রামকিট কেনা হইছিল সোহোর ডেনমান স্ট্রিটের চ্যাস্ ই ফুটে থেকে। গিগস্টার বেজ্ ড্রাম, পুরানা মালিকের হিশাব ছাড়া প্রাচীন একটা স্নেয়ার ড্রাম, হাই হ্যাট, সিম্বলস — এ-ই ছিল আমার প্রথম কিট। একটা বইও দেয়া হইছিল সাথে, যেখানে ফ্ল্যাম প্যারাডিডলস আর র্যাটাম্যাকিউ কীভাবে বাজাইতে হয় সেটা লেখা ছিল (যেটার রহস্য আমি আজও পাঠোদ্ধার করতে পারি নাই)। এইসব বিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্র নিয়া শুরু হয় প্রথম ব্যান্ড হটরডস-এর যাত্রা।
আমাদের এই গ্রুপের লিডগিটারে টিম ম্যাক, রিদমে উইলিয়াম গ্যামেল আর মাইকেল ক্রাইস্কি বেজে ছিল। একজন স্যাক্স প্লেয়ারও ছিল। তার স্যাক্স ছিল পুরানা আমলের কন্সার্ট অ্যা-এর ৪৪০ সাইকেলের সমতুল্য, যেটা নতুন মডেলের থেকে হাফ টোন উঁচা। ফলে এন্সেম্বলের সাথে বাজানো ছিল অসম্ভব। মাইকেল সবার সাহায্য নিয়ে বেজ্ গিটারটা বানায়। খোলাখুলি বললে স্যাক্সোন্সটা হয়তো আরও ভালোভাবে ব্যবহার করা যাইত, কিন্তু আমরা এর লোকদেখানি ভাবটা বেশি নিছিলাম। অ্যাম্প আমাদের হাতের কাছেই ছিল যেগুলা ব্যবহার করা যায়, কিন্তু গ্রুপছবি তুলতে গিয়ে একটা ভক্স ক্যাবিনেট বানাইছিলাম কার্ডবোর্ড বাকশো আর কালি দিয়ে। আব্বাকে একটা ধন্যবাদ দেয়া উচিত এক্ষেত্রে। তার ফিল্মের কাজের জন্যে আমাদের একটা নতুন স্টেরিও টেইপ্ রেকর্ডার পাইছিলাম। ফলে অযথা প্র্যাক্টিসে সময় নষ্ট না-করে আমরা খুব দ্রুত রেকর্ড করা শুরু করে দিলাম। স্টুডিও টেক্নিক হিশাবে ড্রাম আর অ্যামপ্লিফায়ারের আশেপাশে মাইক্রোফোন লাগায়া নানাভাবে চেষ্টা করে একটা কিছু দাঁড়া করাইছিলাম। দুঃখের বিষয় ওই টেইপগুলা এখনো আছে।
হটরডস ‘পিটার গান’ টিভি শো-র থিমের অসংখ্য ভার্শন কাভার করা ছাড়া খুব বেশিদূর আগাইতে পারে নাই কখনোই। ফলে যথারীতি মিউজিশিয়ান হিশেবেও আমার ক্যারিয়ারও মুখ থুবড়ে পড়ল। কিন্তু এরই মধ্যে আমি সারেতে প্রেপ স্কুল থেকে ফ্রেনশ্যাম হাইটসের যৌথ স্কুলে এসে পড়ছি। এইখানে মেয়ে ছিল (আমার প্রথম স্ত্রীর সাথে পরিচয় এখানেই)। আর ছিল জ্যাজ্ ক্লাব, এবং থার্ড ফর্মের পরে লম্বা ট্রাউজারও পরা যাইত। এই ধরনের সফিস্টিকেটেড জীবনই আমি আসলে চাইতেছিলাম।

হটরডস ব্যান্ডের সদস্যরা
প্রেপ স্কুলের তুলনায় ফ্রেনশ্যামে আমার সময় ভালো কাটতেছিল। স্কুলটা ছিল সারেরই হিন্ডহেডের কাছাকাছি বিশাল মাঠ সংলগ্ন বড় একটা কান্ট্রিহাউজ । যদিও ব্লেজার আর পরীক্ষার দিক থেকে বিবেচনা করলে এটা ছিল খুবই ঐতিহ্যবাহী, কিন্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক স্বাধীনচেতা। আর্ট এবং ইংলিশ টিচারদের সাথে আমার খুব প্রিয় কিছু স্মৃতি আছে। সমঝোতা করার দক্ষতাটাও আয়ত্তে আনা শিখতেছিলাম এই সময়েই। ফ্রেনশ্যাম পন্ডের কাছেই স্কুলটা ছিল যেহেতু, একটা নৌকাও জোগাড় করছিলাম। খেলার টিচারকে নৌকা ধার দিয়ে আমি ক্রিকেট খেলা এড়ায়া যাইতাম। এইটার প্রমাণ হচ্ছে সেলোফেন র্যাপিং দিয়ে না-বানায়া আমি দামী একটা ক্রিকেটসোয়েটার দিয়ে নিজের আবিষ্কার-করা কাপড় বানায়া কাজ চালাইতাম।
স্কুলের বলরুমটা ছিল অ্যাসেম্বলি আর অন্যান্য অনুষ্ঠানের জন্যে, কিন্তু কিছুদিন পরপর এর আসল উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করা হতো যখন আমরা ওয়াল্টজ্, ফক্সট্রটস্ আর ভেলেটাস্ নাচতাম। যা-ই হোক, আমার সময়ে ফ্রেনশ্যামের নাচ আস্তে আস্তে লাফালাফিতে পরিবর্তিত হয়ে যাইতেছিল, যদিও নতুন কোনো গান বাজানোর জন্যে অনুমতি নিতে হতো। এর কারণ ছিল পপ মিউজিক যাতে খুব বেশি প্রভাব ফেলতে না-পারে আমাদের উপর। একটা জ্যাজ্ ক্লাবও ছিল। ক্লাবটা শিক্ষকরা বানাইছিল না। এটা ছিল ছাত্রছাত্রীদের ইনফর্মাল গ্যাদারিং। বিখ্যাত হার্মোনিকাবাদক ল্যারির ছেলে পিটার অ্যাডলার আমাদের সাথেই পড়ত। আমার মনে পড়ে সে পিয়ানো বাজাইত, এবং সম্ভবত আমরা একসাথে কোনো সময় জ্যাজ্ বাজানোর চেষ্টাও করছি। আমাদের নিজেদের জ্যাজ্ রেকর্ডগুলা বাজানো কঠিন ছিল বেশ। কারণ স্কুলে একটাই এলপি প্লেয়ার ছিল। আমি যখন প্রায় বের হয়ে যাব তখন ব্যক্তিগত সময় দেয়া হইত রেকর্ড শোনার জন্যে। কষ্টসাধ্য এবং কিছুটা অপছন্দনীয় ব্যাপারগুলা করার থেকে কিছু করার জন্যে ক্লাবই ছিল তুলনামূলক ভালো অপশন। ওইখানে জ্যাজ্ নিয়ে ক্রমবর্ধমান একটা আগ্রহও লক্ষণীয় ছিল।
পরবর্তীকালে আমি ১০০ ক্লাবের মতো লন্ডনের অনেক জায়গায় ঘুরাঘুরি করছি ডাকসাইটে জ্যাজ্ মিউজিশিয়ানদের শোনার জন্যে যারা ইংল্যান্ডের জ্যাজ্ ম্যুভমেন্টের নেতৃত্ব দিতেছিল। এদের মধ্যে ছিলেন লউরি আর কেন্ কয়লারের মতো শিল্পীরা। যা-ই হোক, আমি কখনোই বোলার হ্যাট আর ওয়েস্টকোট পরা গতানুগতিক জ্যাজের আমেজটা পছন্দ করতাম না। বিবপই আমার বেশি ভালো লাগত। আধুনিক জ্যাজের প্রতি আমার আকর্ষণ এখনো আছে, কিন্তু একজন টিনেজার হিশেবে অগ্রসর টেক্নিকগুলা আয়ত্ত করা ছিল সাধ্যাতীত। ফলে ‘পিটার গান’-এর ড্রামের অংশটা ভালোভাবে তুলতে চলে গেলাম।
.ফ্রেনশ্যাম হাইট ছাড়ার পর লন্ডনে আমি এক-বছরের বিরতি নেই একটু ভালোভাবে পড়াশোনা করার জন্যে এবং ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বরে রিজেন্ট স্ট্রিট পলিতে আসি। কিছুটা পড়াশোনা, সেইসাথে পোর্টফোলিওর জন্যে কাজ এবং অনেক লেকচারে অংশগ্রহণ করছিলাম এই এক-বছরে। ইতোমধ্যে নিজের ল্যুক্ নিয়েও এই-সময়ে বেশ মনোযোগী হয়ে উঠছি। খসখসে ডাফল কোট আর শক্ত সুতি ট্রাউজারের প্রতি আমার একটা অনবদ্য ঝোঁক ছিল। পাইপ টানার চেষ্টাও করতাম। আগেকার দিনের লোকেরা যেটাকে বলত ‘বখাইটা’, কলেজের সেকেন্ড টার্মের কোনো-এক দিনে এ-রকম একটা পোলার সাথে আমার কাহিনি শুরু হইল। তার নাম ছিল রজার।
অস্টিন চামি নিয়ে ব্যর্থ দরকষাকষির পর আশ্চর্যজনকভাবে আমাদের মধ্যে এক-ধরনের বন্ধুত্ব গড়ে উঠছিল যার প্রধান ভিত্তি ছিল একই ধরনের মিউজিক টেস্ট। বন্ধুত্বের আরেকটা দিক ছিল স্কুলবিল্ডিঙের বাইরে যে-কোনো জায়গায় যাওয়া। আমরা একসাথে পছন্দের নানা জায়গায় যাইতাম। সেটা হইতে পারত চ্যারিং ক্রস রোডে এদিক-সেদিক ঘুরাঘুরি করে ড্রাম আর গিটার দ্যাখা, ওয়েস্ট এন্ডের সিনেমায় ম্যাটিনি শোতে যাওয়া কিংবা অ্যানেলো ডেভিডসের দিকে যাওয়া। অ্যানেলো ডেভিডস ছিল কনভেন্ট গার্ডেনের ব্যালে শু-মেকার, যারা অর্ডার দিলে কিউবান-হিল্ড কাউবয় বুটও বানায়া দিত। ক্লাসের চাপ থেকে নিজেদের স্বঘোষিত মুক্তি দিয়ে প্রায়ই শুক্রবার সকালে আমরা বের হয়ে যাইতাম উইকেন্ডটা ক্যামব্রিজে রজারের বাসায় কাটানোর জন্যে।

আমার প্রথম গাড়ি, অস্টিন ‘চামি’, হ্যাম্পস্টেড গার্ডেনের বাসার সামনে পার্ক করা
রাজনৈতিকভাবে আমরা প্রায় একই ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছিলাম। আব্বা-মা’র মতো রজারের মাও ছিলেন একজন প্রাক্তন কমিউনিস্ট পার্টি মেম্বার আর লেবার পার্টির কট্টর সমর্থক। আব্বা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিছিল ফ্যাসিজমকে পরাস্ত করার জন্যে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সে পার্টিপোলিটিক্স ছাইড়া দেয় এবং অ্যাসোসিয়েশন অফ সিনেম্যাটোগ্রাফিক টেকনিশিয়ান্সের দোকানে কাজ শুরু করে। একই ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল আমাদের নিজেদের গার্লফ্রেন্ড এবং পরবর্তীকালে বউ — লিন্ডা আর জুডিরও। রজার ছিল কেম্ব্রিজের নিউক্লিয়ার ডিজআর্মামেন্ট ক্যাম্পেইন যুবক সেকশনের চেয়ারম্যান। ও আর জুডি আলডেরম্যাস্টন থেকে লন্ডন পর্যন্ত সিএনডি-র বেশ কয়েকটা মার্চেও যোগ দিছিল। লন্ডনের অদূরে লিন্ডি আর আমি অন্তত একটা মার্চে গেছিলাম কোনো-এক শেষের দিনে। লিন্ডি পরবর্তীকালে গ্রুসভেনর স্কয়ার ডেমোন্সট্রেশনে অংশগ্রহণ করছিল যেটা পুলিশ খুব শক্ত হাতে দমন করে। আমি এখন যেটা বলব সেটা হয়তো রাজনীতি নিয়ে আমার সাধারণ দায়বদ্ধতাটা সম্পূর্ণ বোঝা যাবে — প্রয়োজন অনুযায়ী আচরণ করা ছাড়া আগ্রহশূন্যতার কিছুটা বামে।
রজারের একরোখা হার-না-মানা মনোভাবটা সম্ভবত ওর মা মেরির কাছে থেকে পাওয়া। মেরির ব্যক্তিগত অবিচল মনোভাবের প্রমাণ পাওয়া যায় রজার এবং তার বড়ভাই জনকে দৃঢ়তার সাথে মানুষ করার মধ্য দিয়ে। রজারের বাবা এরিক ওয়াটার্স (পেশায় তিনিও ছিলেন শিক্ষক) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ইতালিতে মারা যান। সিড ব্যারেট আর রজার দুইজনেই ছিল ক্যাম্ব্রিজশায়ার হাইস্কুল ফর বয়েজের ছাত্র। ওইখানে আরও ছিল স্টর্ম থরজার্সন — যে পরবর্তীকালে আমাদের ব্যান্ডের ইতিহাসের তিরিশ বছর গ্রাফিক ডিজাইনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই স্কুলেই রজার কিছু বদমেজাজি টিচার পাইছিল পরে যেটা ‘দ্যা ওয়াল’ অ্যালবামের কাঁচামাল হিশাবে কাজ করছে চরিত্র তৈরি করতে। রজারের মিউজিক নিয়ে চিন্তাভাবনা তখন সেই সময়ের অন্য সবার থেকে খুব আলাদা ছিল না: কিছু গিটার স্ট্রামিং, পুরানো ব্লুজ রেকর্ড থেকে রিফ নেয়া — এইসবের ভেতরেই সীমাবদ্ধ ছিল। আমার মতো ও-ও অ্যামেরিকান ফোর্সেস নেটওয়ার্ক আর রেডিও লুক্সেমবার্গ খুব আগ্রহ নিয়ে শুনত। লন্ডনে কলেজে আসার সময় সে সাথে করে গিটার নিয়ে আসছিল। আমাদের যেসব শেখানো হইত তার খুব ভালো একটা ব্যবহার রজার করছিল লেট্রাসেট দিয়ে। লেট্রাসেট ছিল একটা বিশেষ ডিজাইন টুল যেটা দিয়ে সে ‘I believe to my soul’’ প্রিন্ট করে গিটারের গায়ে সেঁটে দিছিল। সবার চোখে সেটা ছিল খুবই চমকপ্রদ।
গিটার ছাড়াও ভাব নেয়ার মতো রজারের আরও ব্যাপার ছিল। আমাদের ক্লাসের খুব কমসংখ্যক পোলাপানই কলেজে ঢোকার আগে অভিজ্ঞতার জন্যে কোনো আর্কিটেকচারাল অফিসে কাজ করছে। রজার ছিল সেই কয়েকজনের একজন। এই অভিজ্ঞতা তাঁকে অন্য সবার থেকে কিছুটা বিশেষজ্ঞ করছিল ট্রেইনিং আর তার গতিপ্রকৃতি নিয়ে মতামত দেয়ার জন্যে। ক্লাসের বাকি সবার প্রতি তাচ্ছিল্যের একটা ভাব সে লালন করত এবং আমার মনে হয় স্টাফরাও এটা ঠিক পছন্দ করতেন না।

রিজেন্ট স্ট্রিট পলিটেক্নিকে রজার ওয়াটার্সের সাথে প্রথম বছরে
আমাদের এক ক্লাসমেইট, জন কর্পের খুব স্পষ্ট মনে আছে সেই সময়ের কথা — “লম্বা, চিকনা রজার ওয়াটার্সকে দেখলে হাই প্লেইন্স ড্রিফটারের কথা মনে হইত। গিটার সাথে নিয়ে ঘুরত সবসময়। স্টুডিও কিংবা স্টুডেন্ট প্লেয়ার্স অফিসে (ওইটা ছিল পলি ড্রামা ক্লাবের রিহার্সেল রুম) খুব মৃদুভাবে গিটার বাজাইত। আমার কাছে রজার ছিল — সবসময় দূরত্ব নিয়ে থাকবে, মর্বিড লস্ নিয়ে গান গাবে, এই টাইপের কেউ।”
পলিতে প্রায়ই দল বানায়া অ্যাসাইন্মেন্ট জমা দেয়ার কাজ করতে হতো। ফলে প্রথম বছরে আমি আর রজার প্রায়ই জন কর্পের সাথে একটা বাড়ির নকশা করছিলাম। খুব অবাস্তব ডিজাইন হওয়া সত্ত্বেও আমাদের বিল্ডিঙের নকশা বেশ ভালোভাবেই নিছিল সবাই। এটার কারণ জন ছিল খুবই চমৎকার ছাত্র, আর্কিটেকচারই তার ধ্যানজ্ঞান। সে যখন গভীর মনোযোগ দিয়ে ডিজাইন করতেছে, রজার আর আমি তখন ওর কারি আর মিউজিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট নিয়ে ব্যস্ত।
রজারের সাথে কাজ করা খুব সহজ ছিল না। সাধারণত আমি আমার হ্যাম্পস্টেড থেকে উত্তর লন্ডনে যাইতাম পুরা টাউন ক্রস করে। গিয়ে দেখতাম দরজায় নোট ঝুলতেছে ‘Gone to the Cafe des artistes’. ওর থাকারও ঠিক ছিল না। কিছুদিন ও চেলসির কিংস রোডের একটা বাসায় বেনামী বাসিন্দা হয়ে থাকত। গরম পানির কোনো ব্যবস্থা ছিল না, গোসল করা হইত রাস্তার আরেকপাশে চেলসি বাথহাউজে। কোনো ফোনও ছিল না, শুধু ছিল আরও কিছু বেনামী লোকজন। সম্ভবত এই অভিজ্ঞতাই ওকে ট্যুর জীবনের সাথে খাপ খাওয়ায়া নিতে সাহায্য করছে, কিন্তু বাস্তবিকভাবে এ-রকম একটা জায়গায় ড্রয়িংবোর্ড সেট করা ছিল অসম্ভব।
যদিও রজারের লজিঙের দৃশ্য, আওয়াজ, গন্ধ সবই আমার মনে আছে; এই সন্ধিক্ষণে রিকের কথাও মনে পড়ে। ধারণা করি কলেজে পা দেয়ার সাথে সাথে সে মনে হয় বুঝতে পারছিল আর্কিটেকচার তার জন্যে না। রিকের মতে, কোনো-এক ক্যারিয়ারমাস্টার কোনোকিছু না ভাইবাই তাকে আর্কি পড়তে বলছিল। পলিও এটা বুঝতে এক-বছর সময় নিছিল যে আর্কি ওর দ্বারা সম্ভব না। যখন দুই পক্ষই বুঝতে পারল তাদের কারোরই আসলে কিছু করার নাই, রিককে তখন বাধ্য হয়েই অন্য একটা রাস্তা বাইছা নিতে হইল। এবং শেষমেশ ওর স্থান হইল লন্ডন কলেজ অফ মিউজিকে।
ইতিহাস বলে, রিকের জন্ম হইছিল পিনারে এবং ওর বাবা ছিলেন ইউনিগেইট ডেইরির প্রধান বায়োকেমিস্ট। ওদের বাসা ছিল লন্ডনের একেবারে কিনারের হ্যাচ এন্ডে যেখান থেকে রিক হ্যাবেরড্যাশারের আস্কই’স গ্রামার স্কুলে ভর্তি হয়। স্কুলে থাকতেই ও ট্রাম্পেট বাজাইত এবং দাবি করত হাঁটার আগেই সে না-কি পিয়ানো বাজাইত! এবং তারপর বলত — ‘দশ বছর হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি হাঁটতেই পারতাম না।’ বারো বছর বয়সে ওর পা ভাঙে। ফলে প্রায় টানা দুইমাস শুয়ে-বসে কাটায় বিছানায়, সঙ্গীসাথী বলতে ছিল একটা গিটার, কিন্তু কোনো টিউটর ছিল না। রিক নিজের মতো করে কিছু ফিঙ্গারিং করত এই সময়, এবং পরে ওয়েলসের মা ডেইজির অনুপ্রেরণায় একইভাবে পিয়ানোও শেখে। এইভাবে ‘নিজেকে শেখাও’ মেথড ইউজ্ করতে করতেই রিক ওর নিজস্ব সাউন্ড আর স্টাইলটা পাইছিল। এবং এই অভ্যাসই রিককে কখনো মিউজিক স্কুলের টেক্নিক শেখানোর টিচার বানাইতে দেয় নাই।
স্কিফলের সাথে কিছুদিন সময় কাটানোর পর রিক একেবারে ট্র্যাড জ্যাজে ডুবে গেছিল। ট্রম্বন, স্যাক্সোফোন এবং পিয়ানো বাজাইত ও। দুঃখের সাথে জানাইতেছি যে রিক বলছিল — ট্রম্বন বাজাইতে গিয়ে ও না-কি একবার মিউট হিশাবে বোলার হ্যাট ব্যবহার করছিল। সে হাম্ফেরিকে দেখতে লিটলটন, কেনি বলকে দেখতে ইল পাই আইল্যান্ডও গেছিল। ব্রিটিশ আরঅ্যান্ডবি-এর জনকদের একজন সিরিল ডেভিসের দেখা পাইছিল হ্যারোতে এক রেলওয়ে-শুঁড়িখানায়। হাল আমলের ফ্যাশন হিশাবে স্কুটার চালু হওয়ার আগে ও উইকেন্ডে ব্রিংটোনে আসত সাইকেল চালায়া কিংবা হিচহাইক করে। ড্রেস পরত মাস্তিবাজদের মতো — কলারছাড়া শার্ট, ওয়েস্টকোট আর মাঝে মাঝে বোলার হ্যাট। পলিতে ঢোকার আগে সে কোডাকের ডেলিভার অ্যাসিস্টেন্ট হিশাবে কাজ করছে কিছুদিন। ওইখানে ওর কাজ ছিল ড্রাইভাররা যখন ভরদুপুরে গলফ খেলার জন্যে সটকে পড়ত সেটার দেখভাল করা এবং রাত আটটার সময় ডিপোতে ফিরে তাদের হয়ে ওভারটাইম দাবি করা।
রিক সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল — চুপচাপ, ভেতরমুখী একটা ছেলে; পলির বাইরে যার বন্ধুসার্কেল আছে। জন কর্প রিক সম্পর্কে মনে করতে গিয়া বলেন, “রিক ছিল চমৎকার পুরুষালী সৌষ্ঠবের অধিকারী। লম্বা চুল, মনোরম চোখের পাতার কারণে অনেক মেয়ে ওর প্রতি আগ্রহী ছিল।”
পলির প্রথম বছরেই আমরা একটা ব্যান্ড করছিলাম। রিক, রজার আর আমি ছাড়া ওই ব্যান্ডে ছিল ক্লাইভ মেটাকাফ। ক্লাইভ মেটাকাফও ছিল পলিরই ছাত্র যে কেইথ নোবেলের সাথে একসাথে বাজাইত। কেইথ নোবেলও ছিল আমাদের ক্লাসমেইট। আমি নিশ্চিত ক্লাইভের উদ্যোগেই ব্যান্ডটা করা হয়। ক্লাইভ গিটার বাজাইতে পারত আর গান শেখার পেছনে অনেক সময় দিত। কোনো দৃঢ় লক্ষ্য ছাড়াই বাকিরা যোগ দিছিলাম অনেকটা এইভাবে — ‘ও আচ্ছা! আমিও বাজাই একটুআকটু।’ আমাদের প্রথম পলি ব্যান্ড ‘দ্যা সিগমা সিক্স’-এ ছিলাম ক্লাইভ, কেইথ নোবল, রজার, আমি আর রিক। কেইথের বোন মাঝে মাঝে আসত ভোকালে সাহায্য করার জন্যে। রিকের অবস্থা তখন দোদুল্যমান, যেহেতু ওর কোনো ইলেক্ট্রিক কিবোর্ড ছিল না। কোনো পাবে যদি পিয়ানো থাকত, তাহলেই সে বাজাইতে পারত। কিন্তু অ্যামপ্লিফিকেশন ছাড়া ওর পিয়ানোর আওয়াজ ড্রাম আর ভক্স এসি-৩০র আড়ালে চাপা পড়ে যাইত। পিয়ানো না-থাকলে রিক থ্রেট দিত যে ও ওর ট্রম্বন নিয়া আসবে।
রিকের গার্লফ্রেন্ড এবং পরবর্তীকালে বউ জুলিয়েটও একজন গেস্ট আর্টিস্ট ছিল। জুলিয়েটের নানা ব্লুজ ট্র্যাক তোলা ছিল আমাদের সাথে — ও ‘সামারটাইম’ আর ‘কেয়ারলেস লাভ’ গানগুলা ভালোই গাইত। ও ছিল পলির আধুনিক ভাষার শিক্ষার্থী। একবছরের শেষের দিকে ও ব্রাইটন য়্যুনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়, এবং একই সময় রিকও লন্ডন কলেজ অফ মিউজিকে চলে যায়। যা-ই হোক, আমাদের বন্ধুত্ব টিকায়া রাখার জন্যে মিউজিক্যালি অনেক কিছু কমন ছিল। ফলে এইসব কোনো সমস্যা হয়ে ওঠে নাই।
আমি মনে করি ব্যান্ডটা আসলে ভালোর চেয়ে মন্দ প্লেয়ারদের নিয়েই স্থিতিশীল হইছিল। আমাদের মধ্যে একজন ছিল যে কি-না আসলেই বাজাইতে পারত (ভালো বলতেছি কারণ তার একটা সুন্দর ইন্সট্রুমেন্ট আর ঠিকঠাক একটা ভক্স অ্যামপ্লিফায়ার ছিল) এবং কয়েকটা রিহার্সেলের পরই সে কাইটা পড়ে। স্মৃতি বলে, আমরা ফর্মালি কোনো লাইন-আপ দাঁড়া করাইছিলাম না; — যদি দুইজন গিটারিস্ট আসত, গানটা তাহলে একটু ভালোভাবে তোলা হইত (কারণ কেউই প্রপারলি কিছু তুলতাম না)। এই সময় রজার রিদম গিটার বাজাইত। সে পরবর্তীকালে বেজ্ গিটারটা ধরছিল কারণ লিড গিটার কেনার জন্যে এক্সট্রা কোনো টাকা খরচ করতে রাজি ছিল না। আর তাছাড়া সিড ব্যারেট আসার পর বেজ্ গিটারের নিচের পদটাই বাইছা নিছিল। পরবর্তীকালে ও বলছিল, “আল্লা বাচাইছে যে আমাকে ড্রাম বাজাইতে বলে নাই কেউ।” এই কথার সাথে আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট একমত, কারণ ও যদি ড্রামে আসত তাহলে আমাকে রোড-ক্রু হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না…

পলিতে সিগমা সিক্সের প্র্যাক্টিস সেশন
অন্য যে-কোনো শুরুয়াতি ব্যান্ডের মতোই রিহার্সেলের থেকে আমরা বেশি সময় কাটাইতাম গল্পগুজব, পরিকল্পনা আর ব্যান্ডের নাম কী হবে এইটা নিয়া। গিগ্স্ ছিল খুব রেয়ার ঘটনা। ১৯৬৫ সালের আগ পর্যন্ত আমরা কোনো বাণিজ্যিক শোতে অংশগ্রহণই করি নাই। যেগুলা করছি সেগুলা কোনো পাব্লিক অনুষ্ঠান ছিল না। আমাদের বন্ধুবান্ধবদের প্রাইভেট শো-টোতেই বেশি বাজাইতাম। জন্মদিনের অনুষ্ঠান, টার্মের শেষ কিংবা স্টুডেন্টদের নাচের অনুষ্ঠানে বাজানোর কেতা ছিল স্বাভাবিক। পলির বেইজমেন্টের একটা টিরুমে আমরা প্র্যাক্টিস করতাম। এমন সব গান বাজাইতাম যেগুলা পোলাপানদের সাথে যায়। যেমন, ‘আম অ্যা ক্রলিং কিং স্নেইক’ এবং সার্চারের কয়েকটা ট্র্যাক। ক্লাইভের একটা বন্ধু ছিল কেন চাম্পান নামের। ওর লিরিকের উপরেও আমরা কাজ করছি এবং ও এরপর থেকে আমাদের লিরিসিস্ট আর ম্যানেজার হয়ে গেল। ও কার্ড ছাপাইছিল যেখানে নানা পার্টিতে আমাদের বুক করার কথা লেখা থাকত। নানাজনকে ও সেই কার্ড বিলি করত। এটা ছিল আমাদের পাব্লিক পরিচিতি পাওয়ার মাধ্যম। দেখতে আর্কির নার্ভাস স্টুডেন্টের মতো লাগতেছে এ-রকম একটা লাজুক-লাজুক ছবি ছিল ওইটার ভেতরে। একটা আর্টিকেলও ছাপা হইছিল স্টুডেন্ট পেপারে। ওইখানে আমরা রকের থেকে আরঅ্যান্ডবি-র প্রতি আমাদের সমর্থন আর আনুগত্য প্রকাশ করছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের জন্যে কেনের লিরিকের ঝোঁকটা ছিল অনেক বেশিই ব্যালাড-কাম নভেল্টির দিকে। যেমন, ‘তুমি কি কখনো সকালের গোলাপ দেখছো?’-টাইপের (ফার এলিসের সুরে) এবং ‘মাইন্ড দ্যা গ্যাপ’। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে তার লেখাগুলা একজন ভালো প্রকাশককে দেখাইতে সক্ষম হইছিল। গেরি ব্যারোন নামের সেই প্রকাশক আমাদের ব্যান্ড আর গান দুইটারই অডিশন নিতে আসছিল। আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করছিলাম কিন্তু কোনো ধরনের সফলতার মুখ দেখতে পাই নাই। গেরি ব্যান্ডের থেকে গানই বেশি পছন্দ করছিল (যা-ই হোক, এই তথ্যটা কেনেরই দেয়া), কিন্তু গানগুলাও কিছু করতে পারে নাই তাকে অভিভূত করার জন্যে।
সেকেন্ড ইয়ারের শুরুতে, ১৯৬৩-র সেপ্টেম্বরে, ক্লাইভ আর কেইথ সিদ্ধান্ত নিলো তাঁরা ব্যান্ড থেকে বের হয়ে ডুয়ো হিশাবে কাজ করবে। ফলে আমাদের ব্যান্ডের নেক্সট ভার্শন মাইক লিওনার্দের বাসাকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খাওয়া শুরু করে। মাঝতিরিশের মাইক ছিলেন পলির একজন পার্টটাইম টিউটর। আর্কিটেকচারের প্রতি ভালোবাসা ছাড়াও উনি এথনিক পার্কাশন আর রিদম, মুভমেন্ট আর আলোর পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে খুব উৎসাহী ছিলেন। লেকচারে খুব আগ্রহ নিয়ে এইসব বিষয়ে বলতেন। ১৯৬৩-র সেপ্টেম্বরে তিনি হর্নসে কলেজ অফ আর্টে পড়ানো শুরু করেন এবং উত্তর লন্ডনে একটা বাড়ি নেন। উনার কিছু ভাড়াটে দরকার ছিল আয়ের উৎস হিশেবে।
হাইগেটের ৩৯ স্ট্যানহোপ গার্ডেন্স ছিল প্রশস্ত রুম আর হাই সিলিঙের আরামদায়ক এডওয়ার্ডিয়ান ঘরানার বাড়ি। মাইক উপরের তলায় নিজের জন্যে অদ্ভুত সব জিনিশপত্র দিয়ে একটা ড্রয়িং অফিস আর থাকার ঘর বানাইতেছিল, আর নিচতলায় বানাইতেছিল ফ্ল্যাট। সে ছাদের অংশটা খুলে দিছিল, ফলে রিহার্সেল করার জন্যে সেটা হইছিল খুবই আদর্শ জায়গা। কিন্তু সিঁড়িগুলো ছিল খুব খাড়া, ফলে সব যন্ত্রপাতি নিয়ে উপরে যাওয়াটা খুব টাফ একটা ব্যাপার ছিল।
অফিসে মাইককে সাহায্য করার জন্যে পার্টটাইম সাহায্যও লাগত। লন্ডনের কাউন্টি কাউন্সিলের পৃষ্ঠপোষকতায় স্কুলে টয়লেট ব্যাবস্থপনার কাজ করত যেটা বাসার ভেতরে বানানো আলোর মেশিনগুলার নকশা আর তৈরির খরচের অর্থনৈতিক সাপোর্টটা দিতে সমর্থ হইছিল মাইককে। এগুলো বানাইতে জটিল যন্ত্রপাতি সহ অসংখ্য ছিদ্রওয়ালা ধাতব কিংবা কাচের চাকতির প্রয়োজন ছিল। এই চাকতিগুলো বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে ঘুরতে ঘুরতে বিভিন্ন প্যাটার্ন আর রঙের আলো ফেলত দেয়ালে। মাইক বলছিল আমরা যদি তার ওইখানে ভাড়া থাকি তাহলে সবচেয়ে ভালো হয়, ফলে কালবিলম্ব না-করে রজার আর আমি উঠে গেলাম। পরবর্তী তিন বছর রিক, সিড এবং আমাদের অনেক বন্ধুবান্ধব নানা মেয়াদে এই বাড়িতে থাকছে। বিবিসি টিভির টুমরৌস ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টারিতে এই বাড়ির আমেজটা ধরা পড়ছিল, যেখানে দেখাইছিল মাইকের লাইট মেশিন চলতেছে আর আমরা নিচে প্র্যাক্টিস করতেছি (অনুষ্ঠানটা খুব সাহসিকতার সাথে ঘোষণা করছিল ১৯৭০ এর ভিতরেই ব্রিটেনের সব লিভিং রুমে নিজস্ব আলোর মেশিন থাকবে)।

রজার ওয়াটার্স মাইককে সহায়তা করতেছে লাইট মেশিনে
তাঞ্জি আর ম্যাকঘি নামের দুইটা বেড়াল ছিল মাইকের। একটা ছিল বার্মিজ, আরেকটা সিয়ামিজ। রজার আর মাইক দুইজনের বিড়াল দুইটাকে পছন্দ করত ফলে অনেকবছর পর্যন্ত বিড়ালের সাথে রজারের সাথে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমার মনে হয় বিড়ালের জেদি আগ্রাসন রজারের খুব ভালো লাগত। চট দিয়ে বাড়ির সমস্ত দেয়াল ঢাকা ছিল। বিড়ালকে খাওয়ানোর দরকার হইলে শুটকি রাইখা একটা পুরানো মোটর হর্ন বাজাইত। প্রতিবেশীকে জ্বালানো বাদ দিয়া, চিঠির বাক্সের উপর দিয়া লাফাইয়া বেড়াল দুইটা তড়িঘড়ি করে আইসা পড়ত হর্ন শুইনা এবং দেয়াল আর জানলার ধার ঘেইষা পাগলের মতো খাবার খুঁজত। সচরাচর ড্রয়িং-অফিসের সিলিঙের উপরেই খাবারগুলা পাইত তারা।
স্ট্যানহোপ গার্ডেন আমাদের মিউজিকে বেশ বড় ধরনের একটা পরিবর্তন আনে। প্রথম পাকাপাকিভাবে একটা নিজস্ব রিহার্সেলরুম পাইলাম এইখানে আইসা। এবং এ-রকম লাই-দেয়া বাড়ির মালিকের প্রতি আমরা চিরকৃতজ্ঞ। সত্যিকার অর্থেই আমরা মাঝখানে নিজেদেরকে ‘লিওনার্দ লজার্স’ বলে ডাকতাম। ফ্ল্যাটের সামনের দিকের রুমে আমাদের রিহার্সেল চলত, সেখানেই সব যন্ত্রপাতি সেট করা হইছিল। দুর্ভাগ্যবশত, যেহেতু এটা রজার আর আমার বেডরুম ছিল, পড়াশোনা আর ঘুম একেবারে চাঙ্গে উঠল। প্রতিবেশীরা প্রায়ই অভিযোগ করত, যদিও ওই ধরনের সাউন্ড কখনোই হয় নাই। কিন্তু, তারপরেও আমরা রেইলওয়ে-শুঁড়িখানায় গিয়ে রিহার্সেল করতাম তাদের যন্ত্রণা কমানোর জন্যে।
মাইক কখনোই কোনো কমপ্লেইন করে নাই। আসলে বলতে গেলে সে আমাদের একজন অ্যাক্টিভ মেম্বারও হয়ে গেছিল এর মধ্যে। পিয়ানোটা ভালোই বাজাইত সে, এবং আমরা বলেকয়ে তাকে দিয়ে একটা ফারিস্ফা ডুয়ো ইলেক্ট্রিক অর্গান কেনাই। ফলে কিছুদিনের জন্যে সে আমাদের কিবোর্ড প্লেয়ার হয়ে যায়। সেই পিয়ানোটা এখনো আছে। আরেকটা বোনাস ছিল, — হর্নসে কলেজে পরীক্ষাধীন লাইট আর সাউন্ডের বিভিন্ন জিনিশ ব্যবহার করার অনুমতি দিছিল মাইক। রজার অনেক সময় ব্যয় করছিল লাইট মেশিনগুলার পেছনে, ফলত সে মাইকের এক-ধরনের অ্যাসিস্ট্যান্টই হয়ে গেছিল বলা যায়।
কলেজের দ্বিতীয় বছরটা আমরা স্ট্যানহোপ গার্ডেন্সে কাটায়া দেই রিহার্সেল, আর মাঝে মাঝে শো-টো করে, একই সাথে হাল্কাপাতলা পড়াশোনাও। পরবর্তী যে-জিনিশটা আমাদেরকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে তা হলো ১৯৬৪ সালে বব ক্লোজের আগমন। বব ছিল কেম্ব্রিজশায়ার হাইস্কুলের আরেকটা মাল। সিড ব্যারেটের সাথে লন্ডনে আইসা আমাদের দুই ক্লাস নিচে পলিতে ভর্তি হয়। বব সরাসরি স্ট্যানহোপ গার্ডেনে উইঠা যায় কারণ ওই সামারে আমি স্ট্যানহোপ ছাইড়া হ্যাম্পস্টেডে আমার বাসায় উঠি। এটা স্পষ্ট হয়ে গেছিল যে আমি যদি পলিতে থাকতে চাই, তাহলে আমার আরও কাজ করতে হবে। কিন্তু স্ট্যানহোপ গার্ডেনে পড়াশোনা করাটা ছিল অসম্ভব।
গিটারিস্ট হিশাবে ববের বেশ সুখ্যাতি ছিল। ববকে নিয়ে গিটারের দোকানে যাওয়াটাও ছিল আনন্দদায়ক, কারণ নাকউঁচা সেলসম্যান তার বিদ্যুতের গতিতে ফিঙ্গারিং আর মিকি বেকারের জ্যাজ্ কর্ড ধরা দেখে খুব অভিভূত হয়ে পড়ত। যদিও আমাদের মতে সে ফেন্ডার স্ট্রাটোক্যাস্টার বাদে একটু পুরানা ঘরানার সেমি অ্যাকোয়ুস্টিক গিটারের প্রতি দুর্বল ছিল। ববকে নিয়ে মিউজিক্যালি আমরা আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠি, কিন্তু কেইথ আর ক্লাইভ ভোকাল হিশাবে চলে যাওয়ার পর আমরা হন্যে হয়ে একজন ভোকালিস্ট খুঁজতেছিলাম। কেম্ব্রিজের কানেকশনটা আরেকবার ফলল, বব আমাদের সাথে ক্রিস ডেনিসের পরিচয় করায়া দিলো। সে আমাদের থেকে বয়সে একটু বড় ছিল এবং কেম্ব্রিজের মিউজিকসিনের বেশ কয়েকটা ভালো ব্যান্ডের সাথে কাজও করছে। ক্রিস ছিল নর্থহল্টের আরএএফের ডেন্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট। তার নিজের কোনো গাড়ি ছিল না (আমিই ছিলাম ড্রাইভার এবং তখন সেই অস্টিন ‘চামি’ চালাইতাম), কিন্তু ওর নিজের দুই কলাম আর মাইক্রোফোনের নিজস্ব চ্যানেল সহ আলাদা ভক্স পিএ সিস্টেম ছিল। আমরা পিএতে মাঝে মাঝে গিটারও লাগাইতাম। এইসব যন্ত্রপাতির দরুণ ক্রিস খুব সহজেই আমাদের ভোকাল হিশাবে নিশ্চিত হয়ে গেল।
এই ব্যান্ডের নাম দিছিলাম ‘টি-স্টেট’। ফ্রন্টম্যান হিশেবে ক্রিসের একটা ঝোঁক ছিল ওর হার্মোনিকা দিয়ে হিটলারের মোছজাতীয় কিছু-একটা বানানোর আর বলত, “দোস্ত, কিছু মনে করিস না এটা নিয়ে।” এবং প্রত্যেকটা গান ঘোষণা দিত (বব এটাকে বলত বিধ্বংসী আত্মবিশ্বাস) ‘লুকিং থ্রো দ্যা নটহিলস ইন গ্র্যানি-স্ উডেন লেগ’ বলে। ক্রিস যদি ব্যান্ডে থাকত তাহলে হয়তো এটার জন্যে আমাদের জরিমানা গুণতে হইত, যখন আমরা লন্ডনের আন্ডারগ্রাউন্ড বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশে বেশ পরিচিত।

টি-স্টেট ব্যান্ড। বাঁ থেকে : বব ক্লোজ, রিক, রজার, ছাদে ক্রিস ডেনিস, তারপর আমি
ক্রিসের সাথে আমার সম্পর্ক আপনাআপনি চুকেবুকে গেল যখন সিড ব্যারেট নিয়মিত আমাদের সাথে বাজানো শুরু করে। রজার সিড ব্যারেটকে কেম্ব্রিজ থেকেই চিনত — জুনিয়র স্কুলে সিড ছিল রজারের মা’র ছাত্র। লন্ডনে কেম্বারওয়েল কলেজ অফ আর্টে পড়াশোনা শুরু করার আগে থেকেই ওকে আমরা ব্যান্ডের একজন সদস্য করার পরিকল্পনা করছিলাম। ব্যাপারটা ছিল সিড আমাদের সাথে জয়েন করতেছে না, ও নিজেই একটা ব্যান্ডের সদস্য রিক্রুট করতেছে। বব ক্লোজের ভাষ্যমতে, “আমার মনে আছে যেই রিহার্সেলে ক্রিসের ভাগ্য বন্ধ হয়ে যায়। স্ট্যানহোপ গার্ডেনের চিলেকোঠায় ক্রিস, রজার, নিক আর আমি তখনকার কয়েকটা প্রিয় আরঅ্যান্ডবি ট্র্যাক প্র্যাক্টিস করতেছিলাম। সিড একটু দেরিতে আইসা সিঁড়ির উপর থেকে সব দেখতেছিল। কিছুক্ষণ পর সে বলল, ওররে! চরম সাউন্ড! কিন্তু বুঝতেছি না এই ব্যান্ডে আমি কী করতে পারি …”
যদিও সিড শিওর ছিল না ভাল্লাগবে কী না, কিন্তু ও ধরেই নিছিল ওর যোগ দেয়া উচিত। ফলত ক্রিস ডেনিস আর তার পিএ সিস্টেমের দিন ফুরায়া গেল। যেহেতু বব ক্রিসকে রিক্রুট করছিল, রজার সিদ্ধান্ত নিলো ক্রিসকে বাদ দেয়ার সিদ্ধান্তটা ওরই জানাইতে হবে। টটেনহামের কোর্ট রোড টিউব স্টেশনের এক পে-ফোন থেকে ক্রিসকে জানানো হইল আমাদের সিদ্ধান্ত। সেই সময় কোনো-এক কারণে ক্রিস বাইরে ছিল। এবং প্রায় বাই-ডিফল্ট সিড হয়ে গেল আমাদের ফ্রন্টম্যান।
সিডের ছোটবেলার কোনো স্মৃতি না-থাকার কারণে আমি শুধু এইটুকু বলতে পারতেছি আমি যখন ১৯৬৪ সালে ওর সাথে পরিচিত হইলাম, ও ছিল চমৎকার একজন মানুষ। যে-সময়ে সবাই খুব নিষ্পাপ আর আত্মসচেতন হয়ে কুল হওয়ার চেষ্টা করত, সিড ছিল তখন সবার থেকে আলাদা; যতদূর মনে পড়ে প্রথম পরিচয়ের দিন ও নিজ থেকে আমার কাছে আসছিল পরিচিত হওয়ার জন্যে।
কেম্ব্রিজে সিডের বড় হয়ে ওঠা ছিল আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বোহেমিয়ান আর স্বাধীন। সিডের বাবা আর্থর ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় এবং হস্পিটাল প্যাথোলজিস্ট। ওর মাও সবসময় মিউজিক নিয়ে উৎসাহ দিতেন। সিডের প্রথম ব্যান্ড ওদের বাসার সামনের রুমেই প্র্যাক্টিস করত। অনুমতি তো ছিলই, এমনকী ওর বাবা-মা স্বাগতও জানাইছিল ব্যান্ডের কর্মকাণ্ডকে। এই ধরনের আচরণ সিক্সটিজের বাপ-মাদের জন্য ছিল অভাবনীয়। কেম্ব্রিজশায়ার হাইস্কুলে পড়ার সময় ছবি আঁকাতেও সিডের উৎসাহ আর ক্ষমতা ছিল চোখে পড়ার মতো। তবে বাবার মৃত্যুর পর ও কেম্ব্রিজ টেকে আর্ট পড়া ছাইড়া দেয়। ওইখানে সিডের আরেক পরিচিত পাব্লিক ডেভিড গিল্মোর আধুনিক ভাষা নিয়ে পড়াশোনা করত। এই দুইজনের একসাথে ভালোই চলত — লাঞ্চের সময় ওরা একসাথে গিটার আর হার্মোনিকা নিয়ে জ্যাম করত। পরবর্তীকালে ওরা দুইজন কোনো-এক গ্রীষ্মে ফ্রান্সের দক্ষিণে হিচহাইক আর রোদ তাপায়া কাটাইছিল।
সিডের আসল নাম সিড ছিল না, খ্রিস্টীয় রীতি অনুসারে তার নাম ছিল রজার কেইথ। কিন্তু কেম্ব্রিজের রিভারসাইড জ্যাজ্ ক্লাবের স্থানীয় পাবে একজন চরম ড্রামার ছিল Sid Barrett নামের। সিড ওইখানে প্রায়ই যাইত। ক্লাবের নিয়মিত লোকরা নতুন নতুন আসা এই ছোকড়া ব্যারেটের নাম দিয়ে দিলো — Syd Barret, শুধুমাত্র একটা ওয়াই সরানো হইছিল যাতে কনফিউশন এড়ানো যায়।
স্টর্ম থরজার্সনের বয়ানে, সবচেয়ে ইন্ট্রেস্টিং না-হইলেও সিড ওই সময়ের কেম্ব্রিজের একঝাঁক প্রতিভাবান পোলাপানদের মধ্যে একজন। ওই গ্রুপটার সবার মধ্যেই আশেপাশের টাউন আর কান্ট্রিসাইডের সংস্কৃতি আর আভিজাত্যের ছাপ ছিল। সিড ছিল সুন্দর, ছিমছাম, হাশিখুশি — একটুআকটু গিটার বাজাইত আর মাঝে মাঝে জয়েন্ট ফাটাইত। ও যখন লন্ডনে আইসা আমাদের ব্যান্ডে যোগ দেয়, হুট করে আমাদের মিউজিক টেইস্টে কোনো পরিবর্তন হইছিল না। বু ডিডলে, স্টোন্স আর আরএনবি টাইপের গানগুলা সিডের ভালো লাগত, আমরাও এগুলা কাভার করছিলাম। স্টর্মের স্পষ্ট মনে আছে, সিডের বন্ধুবান্ধবেরা যখন বেশিরভাগ রোলিং স্টোন্স পছন্দ করত, সিড তখন সবসময়ই বিটলসের কথাই বলত।

স্ট্যানহোপ গার্ডেনে আমরা। উপরের বাঁ থেকে ক্লকওয়াইজ : বব ক্লোজ, সিড, রজার, রিচার্ড রাইট
স্ট্যানহোপ গার্ডেন যেমন আমাদের রিহার্সেলের সমস্যা দূর করছিল, ঠিক তেমনি পলি দূর করছিল আমাদের পারফর্ম করার অসুবিধা। কলেজে পড়াশোনা নিয়ে আমরা বেশ চাপের মধ্যে থাকতাম। আর্কিটেকচারের কোর্সটার জন্যে ক্লাসের বাইরে, সন্ধ্যায় কিংবা পরে বাসায় আইসা যথেষ্ট শ্রম দিতে হইত। ফলে অন্যকিছুর জন্যে সময় দেয়াটা একটু কষ্টকর ছিল। সপ্তাহ চলাকালীন ক্লাবে কিংবা পাবে যাওয়া ছিল অসম্ভব। কিন্তু শুক্রবার রাতগুলাতে পাবে যাওয়া যাইত সময় বের করে, এবং উইকেন্ডে পলিতে কিছু-না-কিছু হইতই। পলির হলটায়, যেখানে অনুষ্ঠান আয়োজন করা হইত — সেটার একটা জিম জিম ফ্লেভার ছিল। হলের একপ্রান্তে ছিল একটা স্টেজ, যেখানে অনুষ্ঠান আর নাটক নামাইত সবাই। রেকর্ডপ্লেয়ারে তখনকার হিট গানগুলা জোরে জোরে বাজায়া সবাই বপ নাচানাচি করত, কিন্তু মাঝে মাঝে দুই-একটা ব্যান্ডও ভাড়ার চল ছিল।
একমাত্র ঘরোয়া ব্যান্ড হিশেবে আমরা প্রায়ই মূল অনুষ্ঠানের আগে কিছু-না-কিছু বাজাইতাম। এটা আমাদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় ছিল এবং আগ্রহের সাথেই আমরা সুযোগটা নিছিলাম। টুকটাক টাকাও পাইতাম, কিন্তু কখনোই খুব বেশি না — আমাদের ঝোঁকটা ছিল পারফর্ম করার উপরেই। কী বাজাবো এটা নিয়ে তেমন চিন্তাও করতাম না। মাথায় রাখতাম যে স্টেজে উঠতে হবে এবং কিছু কাভার গান বাজাইতে হবে পোলাপান যাতে নাচতে পারে। কিন্তু অন্য প্রফেশনাল ব্যান্ড যারা আসত, তাদের সিরিয়াসনেস দেখে আমরা অভিভূত হয়ে গেছিলাম। তারা যেভাবে পারফর্ম করত সেটা স্পষ্টতই একটা জিনিশ আঙুল দিয়া দেখায়া দিত যে টাকা কামানোর জন্যে নিয়মিত বাজানো আর ছাত্রদের নিয়ে পার্টটাইম পারফর্মারদের মধ্যে পার্থক্যটা প্রায় এক সমুদ্র।
এই ব্যান্ডগুলার মধ্যে ট্রাইডেন্টসের কথা নির্দিষ্টভাবে আমার মনে পড়ে। ওই সময় ট্রাইডেন্টসের গিটারিস্ট ছিল জেফ বেক। এটা ছিল জেফের প্রথম কমার্শিয়াল ব্যান্ড এবং বেশ সুনামও কুড়াইছিল দলটা। ট্রাইডেন্টস ছাড়ার পর ও ইয়ার্ডবার্ডসে এরিক ক্লেপ্টনের জায়গাটা নিছিল এবং নিজেকে অন্যতম সেরা ব্লুজ রক্ গিটারিস্ট হিশাবে প্রমাণ করে এরপর। কিন্তু জেফ ছিল এমন মাল যে ও ‘হাই হো সিল্ভার লাইনিং’-এর মতো ধুমধাড়াক্কা পার্টি-ক্ল্যাসিক করার ক্ষমতাও রাখত।
১৯৬৪-র ক্রিসমাসের কিছু আগে রিকের একটা বন্ধুর সাথে লাইন করে আমরা প্রথম স্টুডিওতে যাই। ওই বন্ধু ওয়েস্ট হ্যাম্পস্টেডের এক স্টুডিওতে কাজ করত এবং ফ্রিতে স্টুডিও ব্যবহার করার সুযোগ দিছিল আমাদের। এই সেশনে আমরা পুরানা আরএনবি ক্ল্যাসিক ‘আম অ্যা কিং বি’ আর সিডের লেখা তিনটা গান (ডাবল ও বো, বাটারফ্লাই, লুসি লিভ) নিয়ে কাজ করছিলাম। ১/৪ ইঞ্চি টেপ আর সীমিত ভাইন্যল প্রেসিং-এ এইগুলা আমাদের প্রধান এবং অমূল্য ডেমো সং ছিল, কারণ অনেক ভেন্যু লাইভ অডিশনের আগে এইগুলা চাইত।
এরই মধ্যে বেশ আশ্চর্যজনক একটা ব্যাপার ঘটে। ‘ইউ আর দ্যা রিজন হোয়াই’ নামের রিকের একটা গান ছিল। অ্যাডাম, মাইক আর টিম নামের তিনজনের ‘লিটল বেইবি’ নামের সিঙ্গেলের বি- সাইডে ওর এই গানটা রিলিজ হয়। ফলে আমাদের বাকিদের কেউ যখন জানতামই না ‘রিপ অফ’ বলতে কী বুঝায় — তার আগেই রিক ৭৫ পাউন্ডের পাব্লিশিং অ্যাডভান্স পাইছিল।
পঁয়ষট্টির বসন্তের শেষের দিকে ১এ প্যালেস গেইট, কেন্সিংটন হাই স্ট্রিটের কাউন্টডাউন ক্লাবে আমরা নিজেদের একটা জায়গায় পাকাপোক্ত করে ফেললাম। ক্লাবটা ছিল একটা হোটেল কিংবা অনেকগুলা ফ্ল্যাটের নিচে। ফলে ক্লাবের শব্দ নিয়ে অভিযোগের একটা সম্ভাবনা সবসময়ই ছিল। কাউন্টডাউনের কোনো বিশেষ থিমের সাজসজ্জা কিংবা স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। এটা একটু কমবয়সী পোলাপানদের টার্গেট করেই বানানো হইছিল। তবে মিউজিকের ব্যাপারটা ছিল অন্যতম, আর বেশ কম দামে ড্রিঙ্ক পাওয়া যাইত। আমার মনে হয় মালিক ধইরা রাখছিল কোনো বিজ্ঞাপন ছাড়াই আমাদের মতো পোলাপানরা এইখানে তাঁদের বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আসবে সাহায্যের জন্যে, আর বন্ধুবান্ধবরা একাই ক্লাবের বারে বসে ফুরফুরা সময় কাটাবে।
আমরা রাত নয়টা থেকে শুরু করে দুইটা পর্যন্ত বাজাইতাম। মাঝখানে বিরতি থাকত বেশ কয়েকটা। বেশি গান তোলা না-থাকার কারণে নব্বই মিনিটের প্রত্যেকটা সেশনে আমরা শেষের দিকে একই গান বাজায়া যাইতাম, তবে অ্যালকোহলে বুঁদ হয়ে থাকার কারণে শ্রোতারা কখনোই বুঝতে পারত না। এইভাবে আস্তে আস্তে বুঝতে পারি যে-কোনো গান সলো দিয়ে ইচ্ছামতো বড় করা যায়। নানা ধরনের গান আমরা নিজেদের মতো করে বাজাইতাম। প্রথমদিকে অ্যামপ্লিফাই করেই বাজাইতাম, কিন্তু দুই-একটা চমৎকার রাত গেছে যখন ক্লাব নয়েজ ইঞ্জাঙ্কশন ইউজ করছে। আমাদের গিগের একমাত্র ভেন্যু হওয়ার কারণে খুবই ডেস্পারেটলি এইখানে পারফর্ম করার চেষ্টা করতাম। উৎসাহের প্রাবল্যে আমরা কর্তৃপক্ষকে বলছিলাম যে আমরা অ্যাকুয়েস্টিক শো করতেও রাজি আছি। রজার কোনোভাবে একটা ডাবল বেজ্ সংগ্রহ করছিল, রিক আনছিল আপরাইট পিয়ানো — অন্যদিকে বব আর সিড অ্যাকুয়েস্টিক গিটার বাজাইত। আমিও ওয়্যার ব্রাশ দিয়া বাজাইতাম। এই সেটে বাজানোর তালিকায় ছিল ববের সিগ্নেচার মার্ক ‘হাউ হাই দ্যা মুন’ আর ‘লং টল টেক্সান’। বাকি গানগুলার নাম অনেক আগে ভুলে গেছি। এই সময়েই আমরা ক্যারিয়ারের জন্যে দুইটা অডিশন দিছিলাম। একটা ছিল বিট সিট নামের ক্লাবে বাজানোর। মেলোডি মেকার নামের সাপ্তাহিক পত্রিকায় তারা এই বিজ্ঞাপন দিছিল (পত্রিকাটা ২০০০ সালে বন্ধ হয়ে যায়)। বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল — ‘Musicians Available and Wanted.’ এটা দেখেই আমরা গেছিলাম অডিশন দিতে, নিজেদের কয়েকটা গান বাজাইছিলাম — কিন্তু তারা আমাদের সিলেক্ট করে নাই।
আরেকটা অডিশন ছিল ‘রেডি স্টেডি গো’ নামের একটা মিউজিক শোতে যেখানে গ্রুভি চ্যাংড়া পোলাপানদের দ্যাখা যাইত গ্রুভি ইয়াং ব্যান্ডের সাথে নাচতেছে। আইটিভি নামের তুলনামূলক নতুন বাণিজ্যিক চ্যানেলে এটা দেখানো হইত। বিবিসির থেকেও একডিগ্রি বেশি র্যাডিকাল ছিল এরা। কিন্তু আফসোসের কথা হচ্ছে ‘রেডি স্টেডি গো!’-এর প্রযোজকরা মনে করছিল সাধারণ পাব্লিকের রুচিতে আমরাও অনেক র্যাডিকাল। তবে তারা অন্তত আমাদের প্রতি আগ্রহ দেখাইছিল, এবং বলছিল এইবার আসলে তারা একটু মেইনস্ট্রিম গান চায় আর-কী! পরের সপ্তাহে তারা আমাদের ইনভাইট করছিল স্টুডিও অডিয়েন্সদের সামনে। অডিয়েন্সদের যেহেতু ক্যামেরার সামনে লাফালাফি করতে দ্যাখা যাইত, সেইজন্যে আমরা কারনাবি স্ট্রিটে গিয়ে শাদাকালো চেকের একজোড়া জ্বলজ্বলা হাউন্ডসটুথ হিপ্সটার ট্রাউজার কিনলাম। এছাড়া ‘রোলিং স্টোন্স’ কিংবা ‘লাভিং স্পুনফুল’ ব্যান্ডের মতো ব্যান্ডগুলাকে লাইভ দ্যাখার একটা মোক্ষম সুযোগও ছিল এইটা।
ক্যারিয়ার নিয়ে আরেক ধরনের চিড়-খাওয়া উদ্যোগ নিছিলাম রক্ কন্টেস্টগুলাতে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে। আমরা দুইটাতে নাম লেখাইছিলাম। একটা ছিল উত্তর লন্ডনের কান্ট্রি ক্লাবে। ওইখানে আমরা আগেও পারফর্ম করছিলাম এবং আমাদের একটা ছোট্ট ফ্যানসার্কেলও ছিল — ফলে অনেক সহজেই আমরা ফাইন্যালে উঠি। কিন্তু এইসময়ে আমরা ঝামেলায় পড়ি। কান্ট্রিক্লাবের থেকে একটু বড় আরেকটা ইভেন্টেও আমরা নাম লিখাইছিলাম — যেটার নাম ছিল ‘মেলোডি মেইকার বিট কন্টেস্ট’ (বিট হুদাকামে ব্যবহার করা ওই দশকের জীর্ণ একটা শব্দ)। ভয়ে ভয়ে আমরা ওইখানে আমাদের ব্যান্ডের কিছু ছবি সহ ডেমো টেপ পাঠাইছিলাম মেলোডি মেইকারে। ব্লু-ইটালিয়ান টাই আর ট্যাব কলার শার্টপরা ছবিগুলা তোলা হইছিল মাইকের বাসার পিছনের বাগানে।
ডেমো আর টাই কাজে দিছিল। কন্টেস্টে চান্স পাওয়ার পর বুঝতে পারলাম আমাদের হিটের সময় আর কান্ট্রিক্লাব কন্টেস্টের ফাইনাল একরাতে পড়ছে। ফাইনালের ডেইট চেইঞ্জ করা যাবে না, আবার মেলোডি মেকারে একজন প্রমোটার প্রত্যেক ব্যান্ডের সমর্থকদের কাছে টিকিট বিক্রি করে টাকা তুলবে ব্যালট বাক্সের জন্যে — তাই হিটের টাইমও চেইঞ্জ করা অসম্ভব। আমরা কোনোরকমে একটা ব্যান্ডের সাথে আমাদের স্লট চেইঞ্জ করে নিছিলাম। নিঃসন্দেহে এটা ছিল সবচেয়ে খারাপ স্লট (যদিও কোনো লাভ হয় নাই, আমাদের ব্যানারে বানান ভুলে লেখা ছিল Pink Flyod); আমাদের পরের স্লটটা যাদের ছিল — সেইন্ট লুইস, ওরা জয়ী হয়ে নিজেরাই বিশ্বাস করতে পারতেছিল না। এবং শেষ পর্যন্ত ওরাই জাতীয় প্রথম পুরস্কার পায়। এইখানে বাজানো শেষ করে তড়িঘড়ি করে গেলাম কান্ট্রিক্লাবে, যদিও লেইট অ্যারাইভালের কারণে আমাদের প্রথম হওয়ার চান্সটা চলে যায়। সারাসিন্স নামের একটা ব্যান্ড প্রথম হয় এবং এইখানেও আমরা বড় ধরনের মারা খাই।
কলেজ টিউটর আর বাপের চাপে বব ক্লোজ ১৯৬৫-র সামারে ব্যান্ড ছাইড়া চলে যেতে বাধ্য হয়। এরপরেও ও লুকায়া বেশ কয়েকবার আমাদের সাথে বাজাইছিল। কেন জানি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে এক্সপার্ট মিউজিশিয়ানটাকে হারায়াও খুব চিন্তিত হইছিলাম না। কোনোকিছু চিন্তা না করার দূরদর্শিতাটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছিল।
আমি এরই মধ্যে লিন্ডির বাবা ফ্রাঙ্ক রাটারের সাথে একবছর মেয়াদী একটা কর্মঅভিজ্ঞতায় যোগ দেয়ার পরিকল্পনা করতেছিলাম তার গিল্ডফোর্ডের আর্কিটেকচারাল অফিসে। রজারকে একটা ধন্যবাদ দেয়া উচিত কারণ ও-ই আমাকে স্ট্রাকচারাল ম্যাথের রহস্যময় বাপারগুলা বুঝায়া দিছিল, তা না-হলে রিটেইক এক্সামে ফেইল করতাম। অন্যদিকে রজার বাইরের একটা এক্সামিনারের কাছ থেকে কমেন্ডেশন পাওয়ার থেকে আরও একবছর থাকার সিদ্ধান্ত নিলো বাস্তব-অভিজ্ঞতার জন্যে। আমার ধারণা রজারের লেকচারের প্রতি যে অনাগ্রহ আর সামগ্রিক একটা অবজ্ঞাসুলভ ভাব ছিল প্রকাশ্যে, স্টাফরাও সেটার মর্ম উপলব্ধি করতে পারতেছিল। তাদের সিদ্ধান্ত ছিল হয় একেবারে প্রতিশোধ, নয় রজারকে একটু খ্যামা দেয়া।
ফ্রাঙ্ক ছিল ভালো আর বাস্তববাদী আর্কিটেক্ট; কিন্তু একই সাথে নতুন ম্যুভমেন্টের একজন সমঝদার। আর্কিটেকচারের সংস্কৃতি আর ইতিহাস নিয়ে ওঁর খুব ভালো দখল ছিল। বলতে গেলে আমি এমন একজনই খুঁজতেছিলাম, ক্যারিয়ারের জন্যে যার সাথে লাইগা থাকা যায়। সে ইউনিভার্সিটি অব সিয়েরা লিওনের পর ব্রিটিশ গায়নার একটা ইউনিভার্সিটি প্রজেক্টে আসে, যেইখানে আমি জুনিয়রদের মধ্যে সবচেয়ে জুনিয়র হিশাবে যোগ দেই। যদিও আমার কাজ খুব কম ছিল, কিন্তু আমি প্রথমবারের মতো বুঝতে পারি এই তিন বছরে ড্রয়িংবোর্ডের উপরে যেসব আঁকছি আর প্ল্যান করছি, সেগুলা কীভাবে বাস্তবায়িত করা যায় তার সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই নাই। আমার আত্মবিশ্বাস একবারে টইলা যায়।
আমি গিল্ডফোর্ডের দক্ষিণে থার্স্লেতে রাটারের হাউজে থাকা শুরু করি। ফ্রাঙ্কের পরিবার, অতিথি থেকে শুরু করে ড্রয়িং-অফিসের কাজ চালানোর জন্যে বাসাটা বেশ বড়ই ছিল। লাগোয়া মাঠে লাঞ্চ ব্রেকে আমরা ক্রিকেট খেলতাম। ফ্রাঙ্ক বাসাটা পরে কাকতালীয়ভাবে কুইনের ড্রামার রজার টায়লরের কাছে বিক্রি করে দেয়।
পুরা শরৎটা আমরা ‘টি-স্টেট’ নাম নিয়েই নানা জায়গায় বাজাইয়া কাটায়া দিলাম, যদিও আমাদের আরেকটা নাম ছিল সিডের দেয়া। নাম নিয়ে খানিকটা ঝামেলাও হইছিল। সম্ভবত লন্ডনের একটু বাইরে নর্থহল্টে, রয়্যাল এয়ারফোর্সের বেইজে বাজাইতে গেছিলাম এরই মধ্যে একবার। গিয়ে দেখি ওইখানে আরেকটা ব্যান্ড একই নামে বুকিং দেয়া। আমি নিশ্চিত না নামটা ওরা আগে দিছে না-কি আমরা, কিন্তু খুব দ্রুত অন্য একটা পথ আমাদের বাইছা নিতে হইল। সিড আরেকটা প্যারা নিয়ে ‘পিঙ্ক ফ্লয়েড সাউন্ড’ নামটা ঠিক করল। পিঙ্ক অ্যান্ডারসন আর ফ্লয়েড কাউন্সিল নামের দুইজন বিখ্যাত ব্লুজ মিউজিশিয়ান ছিল, সেই অনুসারেই এই নাম দেয়া। যদিও আমরা সামান্যই সচেতন ছিলাম তাঁদের ব্লুজ নিয়ে এবং নাম দুইটার সাথে খুব পরিচিতও ছিলাম না। এটা ছিল পুরাপুরিই সিডের আইডিয়া, এবং শেষমেশ কাজ দিলো।
ভাবতে এখন অবাক লাগে হুট করে একমুহূর্তের মধ্যে দেয়া একটা নাম কীভাবে এত দীর্ঘস্থায়ী আর সুদূরপ্রসারী একটা প্রভাব বিস্তার করছে। রোলিং স্টোন্স-এর নামটাও না-কি এইভাবেই আসছিল। জ্যাজ্ নিউজে দেয়ার জন্যে ব্রায়ান জোন্সকে তার ব্যান্ডের নাম দিতে বলছিল, ও নিচে তাকায়া দেখে মাডি ওয়াটার্সের ট্র্যাক ‘রোলিং স্টোন ব্লুজ’ লেখা। ব্যাস, ওইটুকু থেকেই কয়েক দশকের বিক্রিবাট্টা, হাসিঠাট্টা আর সব আয়োজন। আমরা যখন আন্ডারগ্রাউন্ডে বেশ পরিচিত মুখ — ভাগ্য ভালো যে পিঙ্ক আর ফ্লয়েডের এই কম্বিনেশনটা একটা ক্ষীণ সাইকাডেলিক দ্যোতনা দিত আর আমরা হাউলিং ক্রলিং কিং স্নেইকের মতো কোনো নাম দেই নাই।
খুব কমই এ-রকম হইছে টাকার বিনিময়ে আমরা লন্ডনের বাইরে গিয়ে শো করছি। সারেতে ‘হাই পাইন্স’ নামের একটা কান্ট্রিহাউজে আমরা একবার বাজাইছিলাম, আরেকবার ক্যাম্ব্রিজে পঁয়ষট্টির অক্টোবরে স্টর্ম থরজার্সনের গার্লফ্রেন্ড লিবি আর ওর জমজ বোনের ২১তম জন্মদিনের পার্টিতে। আমাদের সাথে আরও ছিল জোকার্স ওয়াইল্ড (গিল্মোর এই ব্যান্ডে ছিল), আর পল সিমন নামের একজন তরুণ ফোকসিঙ্গার। স্টর্মের মতে পার্টিটা প্রজন্মের পোলারাইজেশনটা স্পষ্ট করে দিছিল। লিবির বাবা-মা তাঁদের অনেক বন্ধুবান্ধব দাওয়াত দিছিল যারা স্যুটট্যুট আর বাহারি ড্রেস পরে আসছিলেন। লিবি আর ওর বোনের বন্ধুরা আসছিল ঢিলাঢালা হিপি গিয়ার পরে, জোরে জোরে গান বাজায়া পার্টি গরম করে রাখছিল। কিছুক্ষণ পরে লিবির বাবা তরুণ থরজার্সনকে একটা ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়ে বলছিলেন, ‘এক্ষনি কেটে পড়ো, একেবারে।’
যদিও খুব আশা করছিলাম তেমন না, তবে আমাদের পরবর্তী ব্রেইকথ্রু ছিল ১৯৬৬ সালের মার্চে মার্কুইয়ের একটা গিগ। এটার আগে আমাদের খ্যাতির প্রধান কারণ সিড ছিল আমাদের ফ্রন্টম্যান আর হর্ন্সসে কলেজের লাইট আর সাউন্ড ওয়ার্কশপের বদৌলতে আমরা যা শিখছিলাম তার ভিত্তিতে। নিজেদের গান বলতে ছিল চার-পাঁচটা, যার মধ্যে বেশিরভাগই রেকর্ড করা হইছে ব্রডহার্স্ট গার্ডেন্সে।
এসেক্স য়্যুনিভার্সিটির একটা গিগের মাধ্যমে আমরা প্রথম আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আসি। আমাদের সাথে সেই শোতে ছিল সুইংগিং ব্লু জিন্স আর ম্যারিয়ান ফেইথফুল — যদি কি-না সে ওই সময়ের মধ্যে হল্যান্ড থেকে আসতে পারে — বিজ্ঞাপনে এমনটাই লেখা ছিল, যেটা সবাইকে খুব ভরসা দিতেছিল না। আমরা তখনও টি–স্টেট নামেই পরিচিত ছিলাম, যদিও আমাদের সাইকাডেলিয়াতে রূপান্তরটা ছিল খুব স্পষ্ট। যেহেতু আমাদের লিস্টে ‘লং টল টেক্সান’ ছিল যেখানে আমরা সবাই অ্যাকুয়েস্টিক বাজায়া গাইতাম, কেউ-একজন তারপরেও অয়েল স্লাইড আর ফিল্ম প্রজেকশনের ব্যবস্থা করছিল। কল্পনা করতে পারি ওইখানের কেউই আমাদের মার্কুইয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাটা করে দিছিল …
ক্লাব সার্কিটে ঢোকার জন্যে মার্কুইয়ের সুযোগটা ছিল খুব ভালো, যদিও গিগটা ছিল ট্রিপ কোনো-একটা ফাংশনের যার সাথে ক্লাবের প্রাইভেট বুকিঙের কোনো সম্পর্ক ছিল না। কোনো-এক রবিবার সন্ধ্যায় এই অনুষ্ঠানটার ব্যবস্থা করা হইছিল এবং আমি হলফ করে বলতে পারি কোনো রেগুলার মার্কুই কাস্টমার সেদিন আসছিল না।
সম্পূর্ণ ইভেন্টটাই আমার কাছে খুব আজব ঠেকছিল। আমরা সাধারণত আরঅ্যান্ডবি পার্টিগুলাতে বাজাইতাম যেখানে প্রবেশমূল্য ছিল একপিপা বিয়ার। হুট করে আমরা আসলে বাজাইতেছিলাম কোনো-একটা উপলক্ষ্যে যেখানে আমাদেরকে বড় বড় সলো দেয়ার জন্যে উৎসাহ দেয়া হইতেছিল। কাউন্টডাউন ক্লাবে আমরা বড় বড় সলো দিতাম সময় কাটানোর জন্যে, কিন্তু এটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। মার্কুই ক্লাব আমাদের পরবর্তী রবিবার সন্ধ্যায় একই সময়ে আসতে বললো। এটা আমাদের জন্যে খুব বড় একটা সৌভাগ্য ছিল, কারণ তা না হলে আমরা কখনোই পিটার জেনারের সাথে পরিচিত হইতাম না।
পিটার তখন মাত্র ক্যাম্ব্রিজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করছে, যদিও পিঙ্ক ফ্লয়েডের কোনো মেম্বারের সাথে ওর আগে দ্যাখা হয় নাই ভার্সিটিতে (টাউন আর গাউনের মধ্যে পার্থক্যটা তখনও প্রকট)। লন্ডন স্কুল অফ ইকোনোমিক্সে ও সোশ্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগে চাকরি করত আর সমাজকর্মীদের সমাজবিজ্ঞান আর অর্থনীতি পড়াইত। ডিএনএ নামের একটা রেকর্ডলেবেলও খুলছিল এর মধ্যে। ও ছিল ওর ভাষায় ‘মিউজিকাল নাট’, বিশেষ করে জ্যাজ্ আর ব্লুজে। জন হপ্কিন্স, ফেলিক্স মেন্ডেলসন আর রন অ্যাটকিন সহ কয়েকজনকে নিয়ে ও এই ডিএনএ খুলে মিউজিকে অ্যাভান্দ গার্দ কিছু করার জন্যে। ওর মতে, “আমরা চাইতাম ডিএনএ যাতে খুব অগ্রসরমান কিছু হয়, যে-কোনো অ্যাভান্দ গার্দ — জ্যাজ্, ফোক, ক্ল্যাসিক্যাল, পপ।”
কোনো-এক রবিবারের বাৎসরিক হিশাবের শেষদিকে পিটার প্রায় একগাদা খাতা দেখতে দেখতে হুট করে সিদ্ধান্ত নিলো সতেজ বাতাসে নিঃশ্বাস নেয়ার জন্যে বাইরে যাওয়া দরকার। তার অভিমুখ ছিল ওয়্যারডর স্ট্রিটের মার্কুই ক্লাব। সে জানত ওইখানে একটা প্রাইভেট গিগ হইতেছে। বার্নার্ড স্টোলমান নামের এক বন্ধু তাঁকে জানাইছিল এই খবর। ওর ভাই স্টিফেন ইএসপি নামের একটা অ্যামেরিকান লেবেল চালাইত যারা ফাগসের মতো ব্যান্ডকে প্রমোট করছে। এই ইএসপি ছিল ডিএনএ প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণাস্বরূপ।
পিটারের স্মৃতি থেকে,— “ডিএনএ ফ্রি ইম্প্রোভাইজেশন গ্রুপ এএমএম-এর সাথে কিছু কাজ করছিল, মানে পুরা একটা অ্যালবাম ডেনমার্ক স্ট্রিটে রেকর্ড করা আর-কী! খুবই বাজে ডিল্ ছিল ওইটা। স্টুডিয়োটাইম আর আর্টিস্ট বাদে দুই পার্সেন্ট থাকে এইখানে। একজন ইকোনোমিস্ট হিশাবে আমি হিশাব করে দেখলাম তিরিশ পাউন্ডের একটা অ্যালবামের দুই শতাংশ ছিল মাত্র সাত পয়সা এবং সাতপয়সার বিশাল ভাণ্ডার লাগবে একহাজার পাউন্ড কামানোর জন্যে। এটাই ছিল আমার প্ল্যান। ডিএনএ যদি ভালো কিছু করতে চায় তাহলে অবশ্যই একটা পপ ব্যান্ডকে হাতে নিতে হবে। এর জন্যেই আমি পিঙ্ক ফ্লয়েড সাউন্ডকে দেখতে গেছিলাম মার্কুই ক্লাবের সেই রবিবারে। তবে আমার মনে হইছিল ওদের নামের ‘সাউন্ড’ অংশটা খুবই লেইম।”
“আমার স্পষ্ট মনে আছে শো-টার কথা। ওরা ওই সময়ের বাকি সবার মতো ‘লুইই লুইই’ আর ‘ডাস্ট মাই ব্রুম’-এর মতো আরএনবি বাজাইতেছিল। লিরিক কিচ্ছু বুঝতেছিলাম না, এবং ওই সময়ে কেউ কোনো লিরিক বুঝতোও না। যেটা আমাকে সবচেয়ে আকর্ষণ করছিল সেটা হচ্ছে গানের মাঝখানে গিটার সলোর জায়গায় ওরা বিলাপ করার মতো কোনোকিছু না-বাজায়া খুব অদ্ভুত সাউন্ড বের করতেছিল। প্রথমে আমি বুঝতেই পারতেছিলাম না এটা কী হইতেছে আসলে। এটা ছিল সিড আর রিকের কাজ। সিডের একজন বিন্সন একোরেক ছিল যেটার ফিডব্যাক দিয়ে এমন সাউন্ড আসত। আর রিক খুব অদ্ভুত, দীর্ঘ আর শিফটিং কর্ড বাজাইতেছিল। নিক বাজাইতেছিল ম্যালেট দিয়ে। এই পুরা সেটিংটা দেইখা মনে হইছিল অ্যাভান্দ গার্দ ব্যাপার। শেষ।”
পিটার খুব শীঘ্রই চাচ্ছিল আমাদের সাথে দ্যাখা করতে, এবং বার্নার্ড স্টোলম্যানের বরাতে আমাদের নামধামও জোগাড় কইরা ফেলল। সে সরাসরি স্ট্যানহোপ গার্ডেনে আইসা পড়ছিল আমাদের সাথে দ্যাখা করার জন্যে, “দরোজা ধাক্কানোর পর রজার উত্তর দিছিল। অ্যাকাডেমিক বছর শেষ হওয়ার কারণে সবাই তখন ছুটিতে। তাই আমরা ঐকমত্যে আসলাম ‘সেপ্টেম্বরে দ্যাখা হবে’। রেকর্ডলেবেলটা ছিল আমার বাতিক, তাই অপেক্ষা করতে কখনোই সমস্যা ছিল না। রজার অ্যাট-লিস্ট আমাকে বলে তো নাই ‘ভাগো। চোদায়া মুড়ি খাও।’ ও খালি বলছিল, সেপ্টেম্বরে দ্যাখা হবে।”
পিটার যখন স্ট্যানহোপ গার্ডেনে আসে, আমি তখন প্রথম স্টেইটসে গেছি ঘুরতে। আমেরিকায় আমার ট্যুরটা ছিল মিউজিক্যাল সফরের থেকে আর্কিটেকচার শিক্ষার অংশ হিশেবে — যাতে আমি আমেরিকার বিখ্যাত কিছু বিল্ডিং ঘুরে দেখে আসতে পারি। লিন্ডি তখন ন্যুইয়র্কে মার্থা গ্রাহাম ড্যান্স কোম্পানিতে নাচ শেখায় যেটা আরেকটা উল্লেখযোগ্য কারণ ছিল ভ্রমণের। গ্রীষ্মের ওই সময়ে ওরও ছুটি ছিল। রিকের গার্লফ্রেন্ড জুলিয়েটও কাকতালীয়ভাবে ন্যুইয়র্কেই ছিল ওইসময়।
পানাম ৭০৭-এ করে আমি গেছিলাম আমেরিকায়, ন্যুইয়র্কে ছিলাম দুই-এক সপ্তাহ। কয়েকটা সাংস্কৃতিক আর আর্কিটেকচারের বিখ্যাত স্থান ঘুরে দেখছিলাম— দ্যা গাগেনহেইম, মোমা, দ্যা লেভার বিল্ডিং। এগুলা ছাড়াও কিছু লাইভ মিউজিকও শুনছিলাম। ফাগস, ম্যুজ অ্যালিসন, থেলোনিয়াস সহ অনেককে দেখছিলাম ভিলেইজ ভ্যাঙ্গার্ড আর গ্রিনউইচ ভিলেইজ জ্যাজ্ ক্লাবে। রেকর্ড শপেও ঘুরাঘুরি করছি কারণ অনেক মিউজিকই আমদানি করা হইত না। আর আড়ম্বরহীন অ্যালবামগুলা ছিল খুবই আকর্ষণীয় আর অমূল্য রতনের মতো, যেইখানে ব্রিটিশগুলা ছিল অনেক রঙচঙা। নিরানব্বই ডলারে আমি আর লিন্ডি গ্রেহাউন্ড বাসটিকিট কিনে তিন হাজার মাইলের বেশি ঘুরাঘুরি করছিলাম এককোণা থেকে আরেক কোণায়। আমাদের সাথে সদ্যবিবাহিত এক অ্যামেরিকানের পরিচয় হইছিল। লোকটা ভিয়েতনাম যাচ্ছিল। জিনিশটার মানে আমি তখন বুঝতে পারি নাই সেই ছেষট্টিতে। কিন্তু পরে সামগ্রিক ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বারবার মনে হইত যে মানুষটা বাইচা আছে কি না এখনো।
সামার অফ লাভ হিশেবে সানফ্রান্সিস্কো তখনো খ্যাতি পায় নাই কিংবা হেইট-অ্যাশব্যারি একটা ক্রসরোড মাত্র। শহরটা তখনও সি-ফুড আর দর্শনীয় স্থানের জন্যে পরিচিত। ওইখান থেকে আমরা গ্রেহাউন্ডে করে লেক্সিংটন, কেন্টাকিতে যাই এবং ডন ম্যাকগ্যারি নামের পলির এক বন্ধু আর তার গার্লফ্রেন্ডের সাথে দ্যাখা করি। ডনের তখন একটা পঞ্চাশের শেষের ক্যাডিল্যাক ছিল যেটার ব্রেইকের কোনো ঠিকঠিকানা ছিল না। আমাদের মাউন্টেন পাসিংগুলা আরও উত্তেজনাময় করে তুলছিল এই গাড়িটা। আমরা খুব তাড়াতাড়ি মেক্সিকো চলে গেছিলাম ঘুরতে ঘুরতে, এবং জিনিশপত্রের দাম দেইখা খুব অবাক হইছিলাম। প্রতি রুমের ভাড়া ছিল মাত্র এক ডলার। লেক্সিংটন থেকে ন্যুইয়র্ক, তারপর আটলান্টিক ক্রস করে আবার ফিরে আসার সময়টাও ছিল চরম। এই ট্যুরটার সময় পিঙ্ক ফ্লয়েড সাউন্ড আমার মাথায় তেমন-একটা ছিল না। ভাবছিলাম সেপ্টেম্বর থেকে আবার পড়াশোনার ভেতরে ডুইবা যাব। যা-ই হোক, ন্যুইয়র্কে আমি ইস্ট ভিলেজ নিউজপেপারে দেখি আপকামিং ব্যান্ডগুলা নিয়ে একটা প্রতিবেদন — যেইখানে পিঙ্ক ফ্লয়েড সাউন্ড-এর নাম উল্লেখ করা।
পিঙ্ক ফ্লয়েডের নাম এইভাবে দেইখা ব্যান্ড সম্পর্কে আমার ধারণাটা পুরা চেইঞ্জ হয়ে গেল। যদিও পত্রিকায় যা থাকে তার সবকিছু বিশ্বাস করার কোনো মানে নাই, কিন্তু প্রথমবারের মতো আমার মনে হইল শুধুমাত্র মজার খোরাক হিশাবে নেয়ার বাইরেও আমাদের অসাধারণ কিছু করার সক্ষমতা অবশ্যই আছে।
লেখার সঙ্গে ব্যবহৃত ফোটোগ্রাফগুলো মূল বই থেকে ধারণকৃত এবং অনুবাদকের সৌজন্যে প্রাপ্ত। — সঞ্চালক।